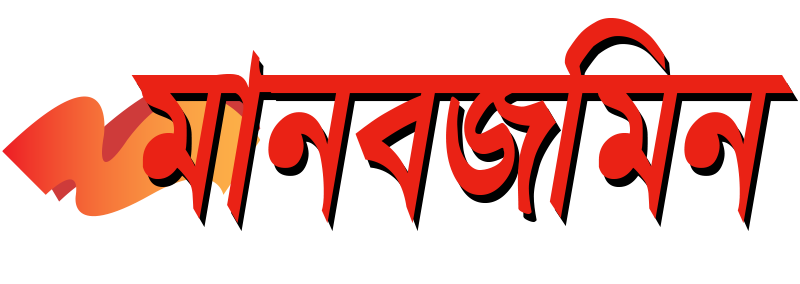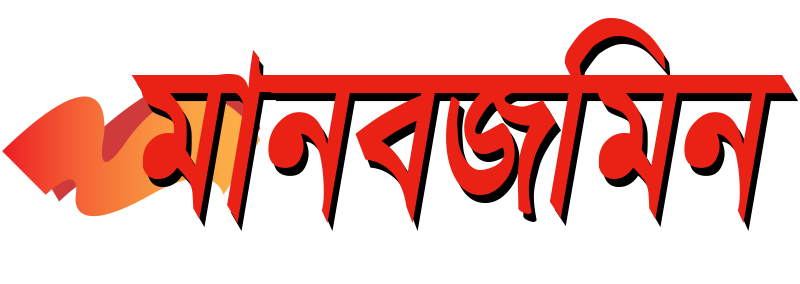ঈদ সংখ্যা ২০২৪
স্মৃতিরা পোহায় রোদ্দুর
মোহাম্মদ আসাফ্উদ্দৌলাহ্
৯ এপ্রিল ২০২৪, মঙ্গলবার
সংগীত মানুষকে এক অবাক আশ্রয় প্রদান করে। মানুষ যখন একাকী হয়ে যায় তখন চারপাশে এসে ছায়ার মতো দাঁড়ায় সংগীত। আমার বেলাতেও ঠিক তাই হলো। নতুন শহরে গানের মধ্যেই খুঁজতে লাগলাম আশ্রয়। সারা বাংলাদেশে একটা আন্তঃকলেজ সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবর্ষের ছাত্র। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো ফজলুল হক মুসলিম হলের মিলনায়তনে। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতে আব্দুল আহাদ, নজরুলসংগীতে শেখ লুৎফর রহমান ও আধুনিক গানে ঢাকা বেতারের এক প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ জনাব নাজমুল হুদা।
নজরুলসংগীত ও আধুনিক বাংলা গানে আমি প্রথম স্থান অধিকার করলাম। আর রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম স্থান পেলেন শান্তিনিকেতন থেকে সদ্য আগত ফরিদা বারী মালিক আর আমাকে করা হলো দ্বিতীয়। অনুষ্ঠানের পরে ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান নির্বাহী আমাকে অডিশন দেওয়ার জন্য ঢাকা বেতার অফিসে আসতে বললেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন লেখাপড়ার পরিবেশ ছিল খুবই উন্নত। গুহঠাকুরতা স্যার ১৯৭১ সালে বর্বর পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।
তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আড্ডা দেওয়ার একমাত্র জায়গা ছিল মধুর দোকান। এই দোকানের হর্তাকর্তা ছিলেন শ্রী মধুসূদন দে। খাবার জন্য পাওয়া যেত চা নামক রঙিন গরম পানি, অখাদ্য ছোট ছোট সন্দেশ। আর পাওয়া যেত টোস্ট বিস্কিট ও গজা। এই যে হাজার হাজার ছাত্র নিয়মিত খেত এই দোকানে তাদের সকলের বাকির হিসাব মুখে মুখে রাখত মধু। তার মাথা তো নয় যেন এক হিসাবের খাতা।
ঈদে বা পূজার ছুটিতে মধুসূদন দে ছাত্রদের দেশের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে আদায় করত পাওনা টাকা। এমনি এক অভিসারে মধু উপস্থিত হলো আমার পিতার মুখোমুখি। সে ফরিদপুরে গিয়ে আব্বার চেম্বারে ঢুকে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল, আমার কাছে নাকি তার ৪৮ টাকা পাওনা আছে। আমি যেহেতু বাকি খেতাম না সুতরাং তার এই হিসাব ছিল একেবারেই মনগড়া এক চাতুরি। আব্বা তো আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই ৪৮ টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন মধুকে। এ কথা জানতে পেরে আমি ভীষণ রেগে মধুর দোকানে উপস্থিত হই ঈদ ছুটির পরপরই। আমি তাকে বললাম, ‘তুমি আমার ৪৮ টাকার হিসাব দেখাও। আর যে মাসের কথা বলছো সেই পুরো মাস তো আমি কলকাতায়ই ছিলাম। অতএব দোকানে বাকি খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।’ বেগতিক দেখে মধু আমার হাতে ২৫টি টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘দাদাবাবু ভুলে যাও সব।’
ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে আমাদের ক্লাসে তিনজন মহিলা সহপাঠী যোগদান করলেন- শামসুন নাহার, মীনা হাকিম ও রাজিয়া খান। বেশ কিছুদিন ক্লাস করার পর আবিস্কার করলাম যে রাজিয়া খানই হচ্ছে আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী রাজু। সেই ছোটবেলায় ফরিদপুরে আমরা অনেক মার্বেল খেলেছি এক সাথে। ওদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি রাস্তার এপারে আর ওপারে। রাজুর মা আর আমার মা ছিলেন ‘সই’। মার্বেল খেলার সময় রাজুর তাক ভ্রষ্ট হতো খুব বেশি এবং সেই অপরাধে তাকে প্রচুর গাট্টা মেরেছি আমি। ওর আব্বা মৌলভী তমিজউদ্দিন খান পরবর্তীকালে পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ক্লাস থ্রি-ফোরের পর রাজুরা প্রথমে ঢাকায় এবং পরে করাচিতে বসবাস করত। সেই ফ্রক পরা ছোট্ট কাঁদুনে মেয়েটি এখন এক পূর্ণ যুবতী। শাড়ি পরা অবস্থায় তাকে কখনো আগে দেখিনি। তাই এত দিন পরে চিনতে কষ্ট হলো। প্রথম দেখায় সে-ও পারেনি আমাকে চিনতে। পরে অবশ্য পরিচয় হলো নতুন করে।
অর্থনীতি বিভাগের আরেক ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হলো তার নাম ডলি। পোশাকি নাম সুফিয়া হুসনে জাহান। মেয়েদের মধ্যে ডলি খেলাধুলায় ছিল পারঙ্গম। বিশেষ করে শট্ পাট্ এবং সাইক্লিংয়ে মেয়েদের মধ্যে সেই ছিল সর্বোত্তম। আমাকে সাঁতারে পারদর্শিতা লাভের জন্য জিমনিসিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম করতে হতো নিয়মিত এবং ওখানেই ইউনিভার্সিটি মাঠে ডলির সঙ্গে দেখা হতো প্রায় প্রতিদিন। ওর একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল। আমার গান তার খুব পছন্দ ছিল। আমাদের মধ্যে আস্তে আস্তে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আমরা দুজনই এই বন্ধুত্বের মর্যাদা সারা জীবন রক্ষা করেছিলাম।
প্রায় তিরিশ বছর আগে ঢাকার বনানী কবরস্থানে গিয়েছিলাম আহাদের কবর জিয়ারত করতে। নিয়তির কী বিধান, আহাদের কবর খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম ডলির কবর। তার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানতাম না বলেই একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কবরের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে তার জন্য অনেকক্ষণ দোয়া করেছিলাম।
ঢাকায় বিশ^বিদ্যালয়ে পড়াশুনায় কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। তাই ছুটে যেতাম আমার মেজ বোনের কাছে মুন্সীগঞ্জে। দুলাভাই সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন মুন্সীগঞ্জে। ছুটি হলেই এক নিঃশ্বাসে ছুটে যেতাম মুন্সীগঞ্জে। মেজ বোনের আদর-যত্নের কোনো তুলনা ছিল না পৃথিবীতে। শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, অমন প্রাণঢালা ভালোবাসা জীবনে বোধ হয় আর কারও কাছে পাইনি। তখন আমার বেশ নামডাক গানে এবং সাঁতারে। এছাড়া আমার কবিতার পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। মুন্সীগঞ্জে আরেকজন ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে প্রথমে ব্যাডমিন্টন খেলতে এবং পরে গান শিখতে আসত। একটা খুব মিষ্টি প্রকৃতির মেয়ে, নাম তার লোটন। পড়ত ক্লাস টেনে। কিছুদিনের মধ্যেই আবিস্কার করলাম মেজ বোনের কাছে এই যে আমার বারবার ছুটে যাওয়া তা কেবল বোনের আদর পেতে নয়, কোথায় যেন আরেকটি ভালোলাগা জন্ম নিচ্ছিল। লোটনদের ঢাকার বাড়িও ছিল গেন্ডারিয়ায়। আমরা থাকতাম দীননাথ সেন রোডে আর ওদের বাড়ি ছিল ডিস্টিলারি রোডে। দূরত্ব ৫০০ গজ। ভালোবাসার চিঠি আসা-যাওয়া করতে লাগল এবং একসময় ওর চাচি আমার মেজ বোনের কাছে বিয়ের প্রস্তাবও নিয়ে আসেন। কিন্তু আমি তখনো ছাত্রাবস্থায় চাকুরিহীন এক বেকার যুবক। ঢাকায় যার না ছিল বাড়ি, না ছিল ঘর। তবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় ছিলাম। সে বিলম্বটুকু লোটনের পরিবারের সহ্য হয়নি এবং তারা মেয়েকে অন্যত্র এক তেল কোম্পানির অফিসারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। সেদিন অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে মেয়েদের শপথের কি কোনো মূল্য নেই? মনে মনে লোটনকে অভিশাপ দিয়েছিলাম সেদিন।

প্রথম পূর্ব পাকিস্তান অলিম্পিকসে ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে স্বর্ণপদক জয় করি ১৯৫৫ সালে। এরপর আন্তঃকলেজ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাদেশিক সকল সাঁতার প্রতিযোগিতায় ব্যাক স্ট্রোকে স্বর্ণপদক বিজয়ী হই এবং পূর্ব পাকিস্তান সাঁতার দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হই। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁতারে ‘ব্লু’ প্রদান করা হয় আমাকে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জাতীয় সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে প্রায় পঁচিশ বছর নিয়োজিত থাকি। পুরনো স্টেডিয়াম পুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং পুল এবং বর্তমানে মিরপুর অবস্থিত জাতীয় সাঁতার কমপ্লেক্স নির্মাণে আমার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সাঁতারের জগতে এসে পরিচিত হই কিছু অসামান্য সাঁতার প্রতিভার সঙ্গে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্রজেন দাস, আব্দুল মালেক, মাহফুজুর রহমান, মোহাম্মদ ইদরিস, আব্দুস সাত্তার, ডক্টর সুলতানুল আজীজ ও মোহসীন ভাইদের সঙ্গে। আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাঁতারকে অন্যতম জাতীয় প্রধান ক্রীড়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হই। বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা সাঁতারু মোশাররফ হোসেনকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলাম আমরাই। মোশাররফের সঙ্গে তুলনীয় সাঁতারু বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি। নিজ যোগ্যতার ফলে সাউথ এশিয়ান সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলাম। এশিয়ান ফেডারেশনে আমার উদ্যোগেই সভাপতি নির্বাচিত হলেন জাপানের বিখ্যাত সাঁতারু ফুরো হাসি। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হলেন ডক্টর সুলতানুল আজীজ। ফুরো হাসিকে আপনারা চিনবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনে ১৯৪৮ সালে। কিন্তু সেখানে জাপানকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি। অথচ তখন পনেরোশ মিটার সাঁতারে বিশ্বে এক নম্বর স্থানে ছিলেন ফুরো হাসি। বিশ্ব অলিম্পিকের পনেরোশো মিটার প্রতিযোগিতা লন্ডনে যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন ঠিক সেই সময় জাপানের টোকিওতে ফুরো হাসি শুরু করেছিলেন তার পনেরোশো মিটার সাঁতার। সেদিনও এই কৃতি সাঁতারু বিশ্ব অলিম্পিকের পনেরোশো মিটারে যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তার চাইতে কম সময়ে এই দুরত্ব অতিক্রম করে ক্রীড়া জগতে প্রতিযোগিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আমরা ক্রমশ একে অন্যের বিশেষ বন্ধুতে পরিণত হই এবং আমি আমি যখন হিরোশিমায় এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হই তখন ফুরো হাসি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং এশিয়ান সুইমিংয়ের শ্রেষ্ঠ অর্গানাইজার হিসেবে একটি স্বর্ণপদক সবার উপস্থিতিতে আমার হাতে তুলে দেন। এটা ছিল আমার সাঁতার জীবনের এক মস্ত পাওয়া। হিরোশিমায় আরও আলাপ হলো বিশ্ব সাঁতার ফেডারেশনের সুযোগ্য সভাপতি জনাব লার ফুই’র সাথে। তিনি ছিলেন আলজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব এতোই ঘনিষ্ঠ হলো যে তাকে আমি বাংলাদেশ জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় মিরপুরের নতুন পুলের উদ্বোধনীতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি ফ্রান্স থেকে ঢাকায় এসেছিলেন এবং আমার বাসায় ডিনার গ্রহণ করা ছাড়াও অনেক সময় গল্প করে কাটিয়েছিলেন। এসব ছিল আমার জীবনের আরেক অধ্যায়। এই অধ্যায়েও প্রত্যক্ষ করেছি খেলার জগতের কূট রাজনীতি, হীন ষড়যন্ত্র, ঘৃণ্য রেসিজম ও অনৈতিক উৎকোচের লীলা। একবার ভারতের সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি কলকাতার জয়ন্ত সেন যিনি ভারতের একসময় একশ’ মিটার স্প্রিন্টে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। ঢাকা থেকে দিল্লি যাবার পথে কলকাতায় এক দিনের যাত্রা বিরতি ছিল। আমি শ্রী জয়ন্ত সেনকে ঢাকা থেকে টেলিফোনে সংবাদটি জানাই এবং তিনি কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত থাকবেন বলে জানান। তিনি বিমানবন্দরে দেখা হতেই বললেন, ‘এর পরের বার আপনি অবশ্যই আমার বাড়িতে একবেলা খাবেন।’ ওইবারই কেন খেতে বললেন না, তা ভাবলে আমার আজও হাসি পায়।
১৯৫৫ সাল। গান-বাজনার প্রতি দারুণ আকর্ষণ। ঢাকায় উচ্চতর সংগীত শেখার মতো না ছিল কোনো প্রতিষ্ঠান, না কোনো ব্যক্তি। তাই ভালো গান শোনার সুযোগ ও সৌভাগ্য থেকে মোটামুটি বঞ্চিত ছিল ঢাকার সংগীত পিপাসু শ্রোতারা। শুনলাম পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর ও মুলতানে এক ঝঁাঁক দুর্দান্ত নতুন সংগীতশিল্পী রয়েছেন। আমরা কয়েক বন্ধু মিলে প্রায় এক লক্ষ টাকা চাঁদা তুললাম এবং মুলতান থেকে ওস্তাদ নাজাকাত আলী খান ও তার ভ্রাতা ওস্তাদ সালামাত আলী খানকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানালাম। তারা রাজি হলেন এবং জুলাই-আগস্টের দিকে তারা এসে পৌঁছালেন। ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে তাদের সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। ঢাকার তৃষ্ণার্থ শ্রোতারা রাত জেগে এই প্রথম উপভোগ করলেন উচ্চাঙ্গসংগীত। সারা রাত চলেছিল সেই অনুষ্ঠান। ওস্তাদ সালামাত আলী খান তার গলার মাধুর্য দিয়ে সে রাতে রচনা করেছিলেন সংগীতের এক মোহজাল। উচ্চাঙ্গসংগীতের এ ধরনের আকর্ষণীয় কণ্ঠশৈলি, রাগ নির্মাণ ও লয়কারি এর আগে কোনো দিন শুনিনি। শেষ রাতের দিকে তারা গাইলেন মিয়াকি মালহার এবং তাল ও লয়কারীর এক অবাক করা দ্যোতনায় সেদিন প্রকৃতিও যেন মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টির ধারায় ঝরে পড়েছিল। টিনের ছাদে যখন বৃষ্টির শব্দ যুক্ত হলো সংগীতের ধ্বনির সঙ্গে তখন ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবাই এক জাদুর শিহরণে চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সমবেত করতালিতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ধ্বনির আরেক তরঙ্গ তুলেছিলেন। ভোর পাঁচটায় যখন সমাপ্ত হলো নাজাকাত আলী ও সালামাত আলীর যুগল পরিবেশনা তখন তাদের ভৈরবি ঠুমরির মুখড়া সুরে বেসুরে সকল শ্রোতার কণ্ঠে অনুরণিত হচ্ছিল। পরবর্তী জীবনে এই দুই ভাইকে কাছে থেকে শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল বহুবার। ঢাকায়, চট্টগ্রামে, বরিশালে। বরিশালে আমার বাড়িতে থেকেই তারা অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নিয়েছিল।
আমার মেজ কন্যার ডাকনাম ‘পূর্বা’। এই নামটি ওস্তাদ সালামাত আলী খানের দেওয়া এবং ওকে যখন জন্মের পর হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় তখন ওর কানে আজানও দিয়েছিলেন সালামাত আলী খান। এখানে বলে রাখা ভালো এসবের কোনো প্রভাবই আমার মেয়ের জীবনে পড়েনি। সে না গাইল গান কোনো দিন, না করল পছন্দ গান-বাজনা। একদিন দু ভাইয়ের কোনো অনুষ্ঠান ছিল না। রাতে ডিনার শেষে প্রায় সাড়ে এগারোটায় তারা আমার গান শুনবে বলে ড্রয়িংরুমে কার্পেটের ওপর বসে পড়ল। রাত সাড়ে এগারোটা থেকে ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত আমার যত প্রিয় গান উর্দু, হিন্দি ও বাংলায় তাদের শুনিয়েছিলাম। কোনো কোনো গান তাদের খুব ভালো লেগেছিল সেই রাতে। যদিও তাদের সামনে বসে এত দীর্ঘ সময় গান করতে আমার অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল।
ফেরদৌসি বেগম বেশ মিষ্টি করে শাস্ত্রীয় সংগীত গাইতে শুরু করে। ওস্তাদ সালামাত আলী খানের কাছে ফেরদৌসি আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ওদের বাড়িতে একটি ছোট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণের এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম।
এই উপমহাদেশের উচ্চাঙ্গ গানের ইতিহাসে সালামাত আলী খান উজ্জ্বলতম এক প্রতিভার নাম। অনেক গুণী শিল্পীর সমাহার ঘটেছে উচ্চাঙ্গসংগীতে, কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পীদের ইতিহাসে। এই মহীরুহুদের মধ্যে রয়েছেন ওস্তাদ আলী আকবর খান, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ বেলায়েত খাঁ, ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খান, ওস্তাদ করিম খান, ওস্তাদ আমীর খান, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান প্রমুখ। অথচ সালামাত আলী খানের লয়কারীর সামনে সবাই যেন অকস্মাৎ থমকে গিয়েছিল। আমার দুঃখ হয় যে সংগীতশিল্পীদের সম্পর্কে আলোচনাকালে ওস্তাদ সালামাত আলী খানকে কেন যেন সবাই এড়িয়ে যান। লতা মুঙ্গেশকর সালামাত আলী খানকে বিয়ে করে তার সঙ্গে লাহোরে গিয়ে বসবাসের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু সালামাত আলী খান এটা সম্ভব নয় বলে লতাকে বারবার জানিয়ে দেন। সালামাত আলী খানের শেষ জীবন কাটে একাকীত্বে ও গভীর বেদনায়। স্ট্রোক করার ফলে তিনি আর গাইতে পারতেন না। সেই অভিমানে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন মৃত্যু পর্যন্ত।
প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করাটা আমাদের রীতির অংশ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ফজলুল হক হলের পুকুর ঘাটেই গাজীউল হকের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ১৯৫৬ সাল ২১শে ফেব্রুয়ারিতে নতুন কিছু করার সংকল্প করলাম আমরা। হলের পূর্বকোণে তিন তলার ছাদে ছিল এক সুউচ্চ গম্বুজ। সাব্যস্ত হলো যে ওই গম্বুজের চূড়ায় ওড়ানো হবে বিশাল কালো পতাকা। আমাদের প্রতিবাদের ভাষা হবে সেই পতাকা। কিন্তু এই ছাদের ওপরে গোল গম্বুজ চড়ে তার শৃঙ্গে পতাকা কীভাবে লাগানো সম্ভব? ডক্টর সুলতানুল আজীজ, জনাব আনিসউদ্দৌলা, কাজী মনিরুজ্জামান ভাই এবং মাহফুজুর রহমান ভাই সমবেতভাবে দায়িত্ব নিলেন পতাকা ওড়াবার। এরা সবাই ছিলেন খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় পারদর্শী। ২০শে ফেব্রুয়ারির গভীর রাতে এরা যে কীভাবে সম্ভব করেছিলেন পতাকা স্থাপন করতে তা আজও আমাদের সকলের কাছে এক বিস্ময় হয়ে রয়েছে। ভোরবেলা পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল হল এবং তারা অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো পতাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে। এরপর তারা নিয়ে এল ফায়ার ব্রিগেড। তারা মই দিয়ে অনেক চেষ্টা করল পতাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে। কিন্তু ব্যর্থ হলো। এরপর এল ইপিআর এবং তারপর সেনাবাহিনী। তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। দৃশ্যটা খানিকটা এ রকম। ফজলুল হক হল ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা, যাদের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ জন হবে। আর তাদের ঘিরে রয়েছে ফজলুল হক হলের ৪০০ ছাত্র। তাদের মধ্যে পতাকা ওড়ানোর সব কজন কারিগর উপস্থিত ছিল। সেনাবাহিনী হলের লনে লাইন করে দাঁড় করালো সব ছাত্রদের। তার মধ্যে ছিল পঞ্চাশের অধিক উর্দুভাষি ছাত্র। তাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করল সেনাবাহিনীর উর্দুভাষি অফিসাররা, যাতে তারা এই কাজের জন্য দায়ী ছাত্রদের দেখিয়ে দেয়। আজ বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে সেদিন তাদের মধ্যে উপস্থিত সকলেই তাদের বাংলাভাষি বন্ধুদের চিহ্নিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আমাদের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি উর্দু ভাষার বিপক্ষের কোনো আন্দোলন ছিল না, ছিল বাংলা ভাষার স্বপক্ষের আন্দোলন। কয়েক দিন চেষ্টা করেও তারা কিছুতেই নামাতে পারেনি সেই পতাকা, যা ওই গম্বুজেই উড়লো আরও এক মাস ধরে যতক্ষণ না বাতাস, বৃষ্টি ও ঝড় পতাকাটিকে বিধ্বস্ত করলো।
ভাবলাম একটু রাজনীতির অভিজ্ঞতা নিই। আমি দাঁড়ালাম হলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে। পোস্টারিং করার খরচ জোগাড় করাও আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। আমার বন্ধুরা পোস্টারের কাগজের খরচ মেটাতে লাগল। আর আমার স্কুলের বাল্য বন্ধু নাহার তখন আর্ট কলেজের তৃতীয়বর্ষের ছাত্র। সারা রাত ধরে নাহার রঙ তুলি দিয়ে বড় বড় পোস্টার লিখতে লাগল আর বন্ধুদের চাঁদার পয়সায় বালতি ভরে চা আর মধুর গজা খেয়ে কাজ করতে লাগল আমার অগণিত চেনা-অচেনা ছাত্র-বন্ধুরা। হঠাৎ একদিন হলের বয়োজ্যেষ্ঠ ৭/৮ জন ছাত্রনেতা আমার তিনতলার কামরায় এসে বললেন যে মুজিব ভাই গাড়িতে বসে আমাকে ডাকছেন হলের গেটে। তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম, সালাম দিলাম। আমার সাথে শেখ মুজিবের এই ছিল প্রথম সাক্ষাৎ। উনি বললেন, ‘তুই নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিস কেন? আওয়ামী লীগের নমিনেশন নে, অনেক ভোটে জিতে যাবি।’ দারুণ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। একহারা পাতলা মানুষ কিন্তু তার গলার আওয়াজ ছিল ভারী ও দরাজ। উনি গাড়ির মধ্যে বসেছিলেন আর আমি বাইরে থেকে হয়েছিলাম তার মুখোমুখি। আমি বলেছিলাম, মুজিব ভাই, আমি একেবারে নির্দলীয় থাকতে চাই। যেহেতু কোনো দলকেই আমার পছন্দ নয়। ওনার উজ্জ্বল মুখটি একটু নিভে গেল। বললেন, ‘ঠিক আছে।’
ফজলুল হক হলে সাতান্ন সালের সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত সমর্থন পেয়েছিল আমার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী নূরুল কাদের খান। তখনকার সময়ে প্রার্থীদের অনেক বক্তৃতা করতে হতো। কখনো কলা ভবনে, কখনো বিজ্ঞান ভবনে, কখনো কমার্স অনুষদে, কখনো আমতলায়, কখনো বেলতলায়, কখনো কার্জন হলে, কখনো মধুর ক্যান্টিনে। বক্তৃতা আবার করতে হতো ইংরেজিতে। যা হোক আমার গান, সাঁতার, নিয়ে যে পথচলা তা কাজে এল ভোটের ফলাফলে। অনেক ভোটের ব্যবধানে আমি জয়ী হয়েছিলাম।
এরপর নূরুল কাদের আমার সঙ্গে কথা বলেনি তিন মাস। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। সাতান্ন সালে অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার পরপরই ম্যানিলায় অনুষ্ঠেয় এশিয়ান গেমসে পাকিস্তান দলের সাঁতারে অংশগ্রহণ করার জন্য তিন মাসব্যাপী এক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করাচিতে শুরু হয়। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টসের দায়িত্বরত ক্যাপ্টেন এম এ রহমান ক্যাম্পে যোগদানের অনুমতি দেন। আসলে তিন মাস ক্লাস কামাই করার অনুমতি দেবার যথাযথ কর্তৃপক্ষ তিনি ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান ছিলেন এই অব্যাহতি দেবার যথাযথ কর্তৃপক্ষ। আমি তা জানতাম না। তিন মাস পরে যখন ফিরে এলাম তখন টার্নার সাহেব চলে গেছেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ডক্টর সাযযাদ হোসেন নামের এক হৃদয়হীন শিক্ষক। তিনি আমাকে ৫৮ সালে মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে দেননি ক্লাসে অনুপস্থিতির কারণে। আমার সহস্র অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও তিনি পরীক্ষায় বসার সম্মতি দেননি। অথচ এই তিন মাস তো আমি আনন্দ ভ্রমণে যাইনি। গিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই উজ্জ্বল করতে। কিন্তু এই নিষ্ঠুর ব্যক্তিটি কিছুতেই আমার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখালেন না। ১৯৭১ সালে এই ভদ্রলোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তার পাকিস্তানি প্রভুদের দয়ায় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ছাত্র মুক্তিযোদ্ধারা সৈয়দ সাযযাদ হোসেনকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক আমার হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব। তিনি ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। দর্শন ছিল আমার সাবসিডিয়ারি সাবজেক্ট। একদিন হঠাৎ করে তিনি ক্লাসে বলে উঠলেন, ‘আরে তুমি তো মাছের মতো সাঁতার কাটো। তুমি তো আমাদের গৌরব। তবে মাঝে মাঝে ক্লাসে এসো, নাহলে পাস করতে পারবে না”। তাঁর স্নেহের কারণে আমি ইংরেজি অনার্স বিষয়গুলির চেয়ে দর্শনশাস্ত্র নিবিড়ভাবে পড়তে শুরু করি এবং সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় দর্শনে প্রথম স্থান অধিকার করি। ড. জিসি দেব একদিন শীতের সকালে ঢাকা হলের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে বললেন, ‘সাঁতার কাটতে হলে ভালো খাওয়াদাওয়া করতে হয়। ওই ক্যান্টিনের শিঙাড়া আর চা খেয়ে শেষ অবধি যক্ষ্মা বাধাবি।’ এই বলে আমার হাত তার হাতের মধ্যে এনে ওনার দীর্ঘ কুর্তার পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আমার হাত ঢুকতে লাগল এবং পকেটের বেশ কিছুটা গহ্বর পার হোয়ে পৌঁছালাম এক কমলার কাছে। উনি বললেন, ‘ওটা বার কর আর আমার সামনে খা।’ সেদিন তাঁর স্নেহাস্পর্শে অভিভূত হয়ের্ছিলাম, চোখ ছলছল করে উঠেছিল। এই মহৎ মানুষটিকে পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী হত্যা করে বাড়ি থেকে গুলি করা মৃতদেহটা দু ব্যক্তি যখন টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল, নিয়তির কী পরিহাস আমি তা অবলোকন করেছিলাম সাত নম্বর বাংলোর গেট থেকে। একমাত্র আমিই জানি ঠিক কোথায় তার মৃতদেহটি মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার ঘণ্টা দুই পরে আমি সাত নম্বর বাংলো থেকে বেরিয়ে সেই মাটিচাপা স্থানে যাই। ডক্টর জিসি দেবকে মাটিচাপা দেওয়ার সময় পানির একটি পাইপ ফেটে যায় এবং সেখান থেকে তির তির করে গোলাপি রঙের পানি বের হতে থাকে যা ছিল ড. দেবের রক্ত মিশ্রিত পানি। জীবনে নিজেকে এতো অসহায় খুব কমই মনে হয়েছে- কেননা আমার করার কিছুই ছিল না।
আরেকজন শিক্ষক ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, যিনি ছিলেন আপাদমস্তক এক রুচিশীল ভদ্রলোক। একবার ক্লাস টিউটোরিয়ালে ‘ট্রাজেডি কেন সাহিত্যের আনন্দময় খোরাক হয়ে ওঠে’-এর ওপরে রচনা লিখতে হয়েছিল। ওই রচনা লেখার জন্য তিনি আমাকে টিউটোরিয়ালে এ প্লাস দিয়েছিলেন যা ছিল খুবই বিরল ঘটনা। আমি হয়ে গেলাম তার স্নেহাসিক্ত ছাত্র। উনি এবং বৌদি কয়েকবার আমাকে তার বাড়িতে খাইয়েছেন। এমন অমায়িক স্বজ¦ন ব্যক্তি আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। ভাগ্যের কী পরিহাস তারও মৃত্যু হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাদের হাতে।
এরপর মনে পড়ে অধ্যাপক বি. সি. রায়ের কথা। তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তি। বিখ্যাত স্কলার হুমায়ুন কবীরের তিনি ছিলেন সহপাঠী। শুনেছি হুমায়ুন কবীর এবং তিনি বাসন্তী নামের এক প্রতিভাবতী নারী সহপাঠীর প্রেমে পড়েন। বাসন্তী নাকি বলেছিলেন যে তোমাদের দুজনকেই আমার খুব পছন্দ এবার এমএ পরীক্ষায় যে প্রথম হবে তাকেই আমি বিয়ে করব। কী দুর্ভাগ্য বি.সি. রায় যদিও অনার্সে প্রথম হন কিন্তু এমএ তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন হুমায়ুন কবীর এবং যথারীতি তার সঙ্গেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন শ্রীমতী বাসন্তী। আর বি. সি. রায় রয়ে যান চিরকুমার। প্রফেসর রায় আমাকে হাতে ধরে কয়েকটি ইংরেজি অক্ষরের ছোট হরফের লেখা কেমন হবে শিখিয়েছিলেন। সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী মানুষ। একটা সাদা ধুতি আর কুর্তা আর একটি কালো পাম্প সু পরেই চিরকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন তিনি। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অপমৃত্যু হয় প্রফেসর বি. সি. রায়ের। তাকে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ছুরিকাঘাত করে জগন্নাথ কলেজের সামনের রাস্তায়। এমন মানুষকে যে কেউ আঘাত করতে পারে এ আমি ভাবতেও পারি না।
আরেকজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে তিনিও ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের সিনিয়র প্রভাষক। সামনে তার চারটে দাঁত না থাকায় উনি ‘থ্রি’ কে ‘শ্রী’ বলতেন। থ্রি ছিল আমার রোল নম্বর। তার নাম জনাব কাজীমুদ্দিন। খুব খিটখিটে মেজাজের কিন্তু তার অন্তর ছিল স্নেহে পরিপূর্ণ। তিনি আমাকে কেন এতো ভালোবাসতেন তা আমি জানি না। পরবর্তীকালে তার মৃত্যুর খবরে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। উনি মধুর দোকান থেকে গজা এনে দুপুরে আমাকে টিফিন খাওয়াতেন। পরে তাঁর ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমি তার সমাধি বাঁধিয়ে দিই। তাঁর মেয়ে (নামটা মনে করতে পারছি না) ছিল খুবই সপ্রতিভ। ফিরোজা আপার গানের স্কুলে ওকে আমি গান শিখিয়েছিলাম কিছুদিন। এখন কোথায় বা কেমন আছে জানি না, তবে খুব জানতে ইচ্ছ করে।
তখন পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়। আমার বেশ নাম ডাক হয়েছে। মাসে ছয়টা প্রোগ্রাম করি রেডিওতে। এছাড়া অনুষ্ঠানে গান করে বেড়াই ঢাকা ও ঢাকার বাইরে। সাঁতারেও খুব নামডাক হয়েছে আবার প্রতি রবিবার পাকিস্তান অবজারভারে আমার ইংরেজি কবিতা নিয়মিত প্রকাশ হতে লাগল। ঢাকায় বোনদের বাসা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছি ফজলুল হক মুসলিম হলে। একটা ভাঙা হারমোনিয়মে ছাদে গিয়ে রেওয়াজ করি। হলের পুকুরে ভোর হতেই সাঁতারের প্র্যাকটিস করি। বন্ধুবান্ধবের সাথে প্রচুর আড্ডা দিই। আর রাত জেগে পড়াশোনা করি। সাঁতার কেটে কোনো অর্থ উপার্জন হতো না, তবে গান গেয়ে বেশ পয়সা কামাতে লাগলাম। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বাড়তেই লাগল। দিনান্তে হলের অসহ্য খাবার পারতপক্ষে খেতাম না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে চলে যেতাম জিন্নাহ অ্যাভিনিউয়ের ‘রেক্স’ রেস্তোরাঁয়। ওখানে খাবার মেন্যু ছিল খুব সীমিত। একটা পরোটা আট আনা আর আট আনায় একটা শিক কাবাব যার ওপর থাকত কিছু শসা আর পেঁয়াজ। এই এক টাকার খাবারে পেট যেমন ভরতো, ভরতো মনও যেহেতু কাবাব পরোটা ছিল দারুণ সুস্বাদু। এক টাকার ডিনার খেয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এবং সমবেত সংগীত পরিবেশন করতে করতে ফিরতাম হলে। এরমধ্যে একদিন শুনলাম যে আমাদের ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের সহপাঠীরা ঢাকার সন্নিকটে অবস্থিত শ্রীপুরে যাচ্ছে পিকনিকে। তবে সেখানে অন্য ডিপার্টমেন্টের দু-একজন ছাত্র যোগ দিলে আপত্তি ছিল না। সাথে মেয়েরাও যাবে আর সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন একজন শিক্ষক। ওদের সঙ্গে ট্রেনে চেপে চলে গেলাম শ্রীপুরে শীতের এক সকালে। শ্রীপুর জঙ্গলে ফরেস্ট বাংলোতে খুব আমোদে কাটলো আমার দিন। ডলি আমাকে যেতে বলেছিল বলেই আমার যাওয়া। আমরা খড়ি কুড়িয়ে আনলাম আর সহপাঠীনিরা তাদের অনভ্যস্ত হাতে রান্না সম্পন্ন করলেন, যা খেতে সুস্বাদু না হলেও অন্য মাধুর্যে ভরপুর ছিল। বিকেলে ক্রিকেট খেলা হলো। মেয়েদের ইমপ্রেস করতে আমরা ব্যাটে বলে দক্ষতা দেখাতে লেগে পড়লাম। তছলিম প্রথম বলেই স্কয়ার কাট মারলো। ক্যাচটি আমি ধরে ফেলেছিলাম বলে ও খুব বিব্রত হলো এবং এজন্য আমার সাথে বেশ কদিন কথা বলেনি। সন্ধ্যা হয়ে এল। এবার আমরা খড়িতে আগুন জ্বেলে চারদিকে চক্রাকৃতি করে আড্ডা শুরু করলাম এবং অনিবার্যভাবে সবাই আমাকে গান গাইতে বলল। অনেকগুলো গান গেয়েছিলাম সেই রাতে। তার মধ্যে একটি গান ছিল, ইন ভিগি ভিগি রাঁতো মে, ইয়াদ তুমহে কিঁউ আতা হ্যা, ঘায়েল দিল ঘাবরাতে হ্যা।’ যার জন্য এই গান গাওয়া যা বোঝার সে আশা করি তা বুঝেছিল। মুখে যা বলতে পারি না, গানে তো তা বলা যায়। ওই দিন রাত্রি যাপন করতে হলো ফরেস্ট ডাকবাংলোর দুটি কামরায়। একটিতে শিক্ষকসহ ছেলে আর একটিতে মেয়েরা। আর মাঝখানে নড়বড়ে এক বাঁশের বেড়া। মধ্যরাতে আমি শুধু ‘গায়ে ঠান্ডা এটা কী লাগল, সাপ নাকি” এই বাক্যটি অন্ধকারে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। বেড়ার দু পাশে নির্ঘুম বন্ধুবান্ধবীরা সব চিৎকার করে দাঁড়িয়ে গেল। মহিউদ্দিন অন্ধকারে লাফ মারলো ওই বেড়ার ওপরে আর মোর্শেদ একটি ছিটকানিতে আঙুল বাঁধিয়ে ঝুলে থাকলো, যা স্বাভাবিকভাবে কোনো শরীরচর্চাবিদের পক্ষেও সম্ভব নয়। আর তার মধ্যে বারবার ডি.এ. রশীদের কণ্ঠস্বর, ‘ওরে বাবারে সাপ।’ মাঝখানের বেড়া ভেঙে পড়ল ওই অন্ধকারে। ইকোনমিক্স বিভাগের যে শিক্ষক দলটির দায়িত্বে ছিলেন তিনি দরজা খুলে বাংলো থেকে লাফিয়ে মাঠের মধ্যে পড়ে ‘ক্যাঁ’ ‘ক্যাঁ’ করতে লাগলেন। এই কোলাহল আর চ্যাঁচামেচির মধ্যে নিশ্চিন্তে শুয়েছিলাম শুধু আমি।
হইচই শুনে ডাকবাংলোর অদূরে অবস্থিত দারোয়ানদের ঘর থেকে কয়েজন ছুটে এল হারিকেন নিয়ে। পরদিন সকালে শ্রীপুর থেকে ট্রেনে চেপে ঢাকায় ফিরে আসি। মেয়েরা নাকি পরে বলেছিল, আসাফই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী তার সাপের কোনো ভয় নেই। হায়রে মিথ্যার জয়।
এর মধ্যে আমাদের ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটর বেলায়েত হোসেন ভাইয়ের কাছে শুরু করলাম বক্সিং শেখা। কিছুদিনের মধ্যে বক্সিংয়ে বেশ ভালোই উন্নতি করতে লাগলাম। গায়ে তখন ভীষণ জোর। বুক ভরা সাহস, অক্লান্ত দেহ। তাই আঘাত নেবার ক্ষমতাও প্রচণ্ড। তবে এটা খুব নিষ্ঠুর এক খেলা, যা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হলেও আমার মনে হয় অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। কেননা দুজন মানুষ মরিয়া হয়ে লড়বে তাদের দাঁত ভেঙে যাবে, নাক ভেঙে যাবে, ঠোঁট কেটে যাবে আর একপাল দর্শক তা দেখে পুলকিত হবেন সেটা সভ্য সমাজের কোনো খেলা হতে পারে না।
সারাদিন এত খেলাধুলা করে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পেতাম না। জিমনেশিয়াম থেকে ক্লান্ত হয়ে হলের ক্যান্টিনে গিয়ে বাদাম তেলে ভাজা শিঙাড়া আর চা খেয়ে দিনে দিনে কেমন যেন এক ক্লান্তি বাসা বাঁধতে লাগল। আসলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমার বুকে যক্ষ্মা রোগ ক্যালসিফাইড হয়ে বাসা বাঁধল, যার চিকিৎসা হলো আরও তিরিশ বছর পরে। যখন ক্যাসিফাইড যক্ষ্মার বীজ ক্যাপসুল ভেঙে বার হয়ে এল। সেসব কথা পরে বলব।
গানের জীবন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেই শুরু হয়। তখন ঢাকায় কোনো টিভি ছিল না। ছিল শুধু বেতার। যেখানে আমি, আবু বকর ও আনোয়ার উদ্দিন খান ও খালেদ হোসেন সমসাময়িক ছিলাম। অত্যন্ত প্রতিভাধর আবু বকর দু-এক বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। আনোয়ার উদ্দিন খানও ছিল এক অত্যন্ত মেধাবী গায়ক। সেই সাথে যোগ দিল আবু হেনা মোস্তফা কামাল। আমাদের সময় আবু হেনাই ছিল শ্রেষ্ঠ গীতিকার। তবে মোহাম্মদ মনীরুজ্জামানও খুব ভালো গীতিকার ছিলো। এটা খুব আক্ষেপের কথা যে কবি হিসেবে আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রতি সমসাময়িক সমাজ সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। কবি হিসেবে প্রতিভার দিক থেকে তাকে আমি শামসুর রাহমানের ওপরে মূল্য দিই। রোমান্টিক কাব্যরস সৃষ্টিতে এবং শব্দ চয়ন ও উপমা সৃষ্টিতে তার মতো মেধাবী কবি এ দেশে আমি আর কাউকে দেখি না। ব্যক্তিজীবনেও আবু হেনা ছিল কাজী নজরুলের মতোই বেপরোয়া ও সাহসী। তার গীতি রচনায় পাওয়া যেত গভীর কাব্যের হাতছানি। আর তার কবিতায় পাওয়া যেত এক সুখময় গীতিময়তা। আমি অবাক হয়ে যাই যে বাংলাদেশে যখন কবিতা নিয়ে আলোচনা হয় তখন আলোচকরা এক পাল মিডিয়োকার কবিদের নিয়ে ব্যর্থ উচ্ছ্বাসে মত্ত হন। আরেক পাল আছেন মিডিয়োকার সমালোচক। অথচ উচ্চারিত হয় না আবু হেনার নাম একবারও। বাংলাদেশে সংস্কৃতিচর্চায় নিয়োজিত কিছু কনট্রাক্টর আছেন এবং তারা তাদের দলভুক্ত ব্যক্তিদের ছাড়া আর কারও প্রতি নজর দেন না। এমনটি হয়ে আসছে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে। এমনি হয়তো হতে থাকবে আরও কয়েকটা পঞ্চাশ বছর।
ঢাকা বেতারের সঙ্গে পঞ্চাশের মধ্যভাগে আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। কয়েকজন গুণী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে এ সময়কালে। এদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে মীর কাসেম খানের কথা। সেতারে তার মতো পারদর্শী বাদক পূর্ব পাকিস্তানে বা এখনকার বাংলাদেশে কাউকেই দেখিনি। লাজুক স্বভাবের এই গুণী শিল্পী আমার গানের সঙ্গে যখন বাজাত তখন বেশ কিছুটা সময় আমি ইচ্ছে করে সেতারের জন্য ছেড়ে দিতাম যাতে গানের সুরের ওপরে মীর কাসেম আরও কিছু মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে। বাহাদুর হোসেন খান মীর কাসেমেরই ফার্স্ট কাজিন। সেও তখন ঢাকা বেতারে সেতারই বাজাত বেশি। পরে অবশ্য তারা দু ভাই বাজনায় আরও তালিম নেবার জন্য তাদেরই আরেক ভাই সরোদ সম্রাট ওস্তাদ আলী আকবর খানের কাছে শিক্ষালাভের জন্য কলকাতা চলে যায়। সময়টা ১৯৫৬ সাল। বাহাদুর হোসেন খান সেতার ছেড়ে সরোদ বাজাতে শুরু করলেন এবং শত প্রতিঘাতেও দমে না গিয়েও টিকে থাকলেন আলী আকবর খানের শিষ্যত্বে। আর হয়ে উঠলেন ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান। তিনি কলকাতাতেই থেকে গেলেন এবং অত্যন্ত কম বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বাহাদুর হোসেনের চাইতেও অনেক বেশি প্রতিভাধর ছিল মীর কাসেম। কিন্তু সে পরিবার ছেড়ে আর্থিক কষ্টে কলকাতায় থাকতে পারলো না এবং তিন মাস পরেই ফিরে এল ঢাকায়। ও যদি ফিরে না আসত আর আলী আকবর খান সাহেবের সাহচর্যে ৫/৬ বছর থাকতে পারত, তাহলে এই উপমহাদেশ উপহার পেত এক অনবদ্য সেতার শিল্পীকে। আমি কৃতি বাদকদের অনেক বাজনা বহুকাল ধরে শুনেছি। মীর কাসেমের প্রতিভা বিখ্যাত সেতার বাদক নিখিল বন্ধ্যোপাধ্যায়ের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না বলে আমি নিশ্চিন্ত বলতে পারি। তিন মাস পরেই মীর কাসেমকে আবার ঢাকায় দেখে আমি তো হতবাক। কেননা যাবার সময় সে আমাকে বলে গিয়েছিল আলী আকবর খানের কাছে শিক্ষার সমাপ্তি না ঘটিয়ে সে আর দেশে ফিরবে না। আমাকে আড়ালে নিয়ে মীর কাসেম বলেছিল, কলকাতায় তার কোনো থাকার জায়গা ছিল না। এমনকি সস্তা হোটেলেও থাকা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। তাই ব্যর্থ মনোরথে এক বুক বেদনা নিয়ে সে ফিরে এসেছিল ঢাকায়। মীর কাসেমের চোখে ছানি পড়ল অথচ এত বড় শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তার চোখের চিকিৎসা করাবার সামর্থ্য ছিল না। আমাকে বলল বিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ড. টি আলীর কাছে নিয়ে যেতে। সৌভাগ্যক্রমে আমি যে ভাড়া বাসায় কিছুদিন থাকতাম, সেই বাড়িটি ড. টি আলী সাহেবের বাড়ির পেছনেই ছিল। আমার এক কামরাওয়ালা বাসায় রেখে তার চক্ষু চিকিৎসা করালাম। টি আলী সাহেব তখন সবচেয়ে নামী ও দামি চক্ষু চিকিৎসক। তিনি মীর কাসেমের চোখের অপারেশন করলেন এবং মীর কাসেমের সুখ্যাতির কারণে কোনো টাকা নিলেন না। তারপর চল্লিশ দিন মীর কাসেমকে গোসল করিয়েছি আমি, খাইয়েও দিয়েছি আমি, যেহেতু তার দু চোখেই ব্যান্ডেজ করা ছিল। তবে অসুবিধা হতো তাকে নিয়ে বাথরুম করানোর। কিন্তু আমি ওকে এতো ভালোবাসতাম যে কোনো কষ্টকেই কষ্ট মনে হয়নি। এই ঘটনার মাত্র সাত/আট বছরের মাথায় মীর কাসেম এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। ওকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। এমন অনেক ঘটনাই মনে দাগ কেটে আছে, দাগ কেটে থাকবে চিরদিন।
হঠাৎ করে ঘোষিকা হিসেবে ঢাকা বেতারে যোগদান করেন দিলারা হাশেম। সুন্দর, সপ্রতিভ ও অত্যন্ত মিশুক ছিলেন তিনি। আমার গান নাকি তার খুব ভালো লাগত এবং আমার অনুষ্ঠানগুলির ঘোষণা তিনিই করতেন। একদিন বললেন, ‘আপনার কাছে গান শিখবো।’ কিন্তু শেখার জায়গা না থাকায় নিচের তলার তিন নম্বর স্টুডিও খালি থাকলে সেখানেই পিয়ানোর পাশে বসে সুধীরলাল চক্রবর্তীর অনেকগুলো জনপ্রিয় গান তাকে শিখিয়েছিলাম। তিনি এলেই রেডিও স্টেশনে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হতো। প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভরা তার সঙ্গে গল্প করার আগ্রহে নিজেদের কর্তব্য বিস্মৃত হতেন। পরে এক সহপাঠীকে বিয়ে করে তিনি আমেরিকায় চলে যান। এই কয়েক মাস আগে লোকমুখে শুনলাম দিলারা হাসেমও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি হলে চলে যেতাম ফরিদপুর। সেখানে গিয়ে মন টিকত না। যেহেতু সঙ্গী সাথীরা লেখাপড়া বা জীবিকার খোঁজে সবাই চলে গেছে শহর ছেড়ে। যেতাম কলকাতায়, যাবার পেছনে গান শেখার উদ্দেশ্যটাই ছিল মুখ্য। সেজ বোন ফিরোজা বেগম তখন কলকাতাতেই থাকতেন। কিংবদন্তি সুরকার ও সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে তত দিনে তার বিয়ে হয়ে গেছে। কমল দা আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং প্রায় প্রতি রাতে বাসায় ফেরার পথে আমজাদিয়া কিংবা আমানিয়ার ‘চাপ’ আমার জন্য নিয়ে আসতেন। তারা তখন থাকতেন পার্ক স্ট্রিটের বিল্টমোর হোটেলে। কিন্তু তিনি এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে গান শিখবার জন্য ওনাকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ওনার সঙ্গে গানের রিহার্সাল শুনতে যেতাম এবং সেখানে বড় বড় শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা করার এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের রিহার্সেলের গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। সেখানে দেখেছি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে, তালাত মাহমুদকে এবং আরও অনেক শিল্পীদের। তাদের গান গাইবার ভঙ্গি, মাইকের সামনে গাইবার কৌশল, গানের বাণীর সঙ্গে নিশ্বাস নেবার সঠিক পদ্ধতি এগুলো দেখে সেগুলো আয়াত্ত করার চেষ্টা করতাম নিজে। গানে শুধু সুর, লয় আর তালই যথেস্ট নয়। গানের অলংকার আছে। সুরকে সাজিয়ে তুলতে হয় এসব অলংকারের সাহায্যে। যেমন মীর, খটকা, মুড়কি, গ্যম্যক, আন্দোলন, ন্যস, ওঙ্কার ইত্যাদি। এগুলি ব্যবহার না করলে অলঙ্কারহীন সুর ধারণ করে বিধবার বেশ। এসব আমার গাইবার ক্ষেত্রে দারুণ উপকারে লেগেছিল। এই ছোট ছোট বিষয়গুলোর মধ্যেই গড়ে ওঠে এক শিল্পীর সাথে অন্য শিল্পীর পার্থক্য। যেমন উচ্চারণের ক্ষেত্রে ‘ফ’-এর উচ্চারণ অনেক শিল্পীরই ত্রুটিপূর্ণ। কিছু শব্দ নব্বই ভাগ কণ্ঠশিল্পী যথার্থভাবে গাইতে গিয়ে উচ্চারণ করতে পারেন না। যেমন: ‘তোমার’ কী ‘আমার’ গাইতে গিয়ে বেশির ভাগ ‘তোমা’ এবং ‘আমা’। এখানে ‘র’ এর উচ্চারণ প্রায়ই স্পষ্ট নয়। সংগীতের মূল বিষয়টিই হচ্ছে দম আর বাতাস। অথচ গাইবার সময় শব্দগুলির মধ্যে কোথায় নিশ্বাস নিতে হবে তা কিন্তু অধিকাংশ শিল্পীরই জানা নেই। কমল বাবুর চাইতে বেশিসংখ্যক জনপ্রিয় গান সুর করেননি আর কোনো সুরকার। দু-দশটা হিট গান রচনা করেছেন অনেক সুরকার। কিন্তু শত শত গান জননন্দিত করতে পেরেছেন একমাত্র কমল দাশগুপ্ত। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাস করে যে আধুনিক বাংলা গান কাদের হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, তাহলে আমি এই অনুক্রমে তাদের নামকে সাজাব। কমল দাশগুপ্ত, সুধীরলাল চক্রবর্তী, শচীন দেব বর্মন ও সলিল চৌধুরী। এরা নেই বলেই আজ বাংলা গানের এমন দৈন্যদশা।

আমাকে ওস্তাদ কাদের জামিরি সাহেব হঠাৎ করে তলব করেছিলেন ফিল্মে গান গাইতে। উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কলকাতার বিখ্যাত ওস্তাদ জমির উদ্দিন খান সাহেবের তিনি ছিলেন ভ্রাতুস্পুত্র। এই ছায়াছবিটির নাম ছিল ‘তোমার আমার’। পরিচালক ছিলেন মনসুর ভাই। প্রযোজনায় আব্দুল হামিদ। ঢাকায় তখন গানের রেকর্ডিং সুবিধা ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাই গানগুলোর রেকর্ডিং হলো লাহোরে মালিকা স্টুডিওতে। সঙ্গে কাদের জামিরি সাহেব ও তার সহকারী ধীর আলী মিয়া। মেয়ে গায়িকা ছিল ফেরদৌসি বেগম। দিন দশেক লাহোরে বেশ কাটলো। আমাদের রেকর্ডিং সম্পন্ন হলো। আমার ছিল দুটি গান, যার একটি আবু হেনার লেখা ‘আয়না আছে’ আর আরেকটি আহসান হাবীবের লেখা ‘আহা আমার সোনার দেশ’। দুটি গানই তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফেরদৌসির দুটি গানও সুন্দর গাওয়া হয়েছিল। আমরা শালিমার উদ্যান ঘুরে দেখলাম, খোলা বাজারে গিয়ে কিছু শপিং করলাম তারপর আমি ফিরে এলাম ঢাকায় আর ফেরদৌসি গেল বোধ হয় মুলতানে একটি সংগীত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য। ফেরদৌসি বেগম তখনো ফেরদৌসি রহমান হয়নি। ও ছিল সলাজ, সপ্রতিভ একটি মেয়ে। তাকে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির বলেই আমার মনে হয়েছে। ফেরদৌসি কথাবার্তায় ছিল অত্যন্ত মার্জিত। কথাবার্তার মতো ওর স্বভাবও ছিল খুব মিষ্টি। ওকে বেশ ভালো লেগেছিল।
ছাপান্ন সালের দিকেই কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছিল খুরশিদ আনোয়ার। দেশভাগের বেশ পরে ওদের পরিবার কলকাতা থেকে বাংলাদেশে চলে আসে। ওদের বাড়িও ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারিপুরে। খুব ভালো টেবিল টেনিস খেলত আনোয়ার। সেও এসে ফজলুল হক হলেই উঠল। পরিচয় হওয়ার সময় থেকেই খুব দ্রুত এক গভীর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় আমাদের মধ্যে। আমার মা ফরিদপুর থেকে নিয়মিত হালুয়া ও লাড্ডু পাঠাতেন হলে। একটি টিন নির্দিষ্ট থাকত খুরশিদের জন্যও। আমরা এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলাম যে অনেকেই ভাবত আমরা দু ভাই। আমার বিয়ের পর আমার স্ত্রী খুরশিদকে আপন করে নিয়েছিল নিজের ভাইয়ের মতো। কিন্তু খুরশিদ যখন বিয়ে করল রুইদা নামক পাকিস্তানের এক পাঠান মেয়েকে তখন থেকেই দূরত্ব বাড়তে থাকে। রুইদা আমাদের সম্পর্ক সহ্য করতে পারেনি প্রথম দিন থেকেই এবং যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমার পরম বন্ধু চিরতরে আমার থেকে দূরে সরে যায়। এখন তো আমাদের মধ্যে বাক্য বিনিময়ও বন্ধ। রুইদা জিন্দাবাদ।
মনে পড়ে মাকিন আহমেদের কথা। প্রাণীবিদ্যার ছাত্র। সব সময়ে কাপড়চোপড়ে থাকত কেতাদুরস্ত। একটু হাসলেই ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ত। সদাহাস্য এই মানুষ ঘন ঘন প্রেমে পড়ত। তাকে দেখে কেউ একটু হাসলেই সে ভাবত যে মেয়েটির ওকে খুব পছন্দ। হাসির আড়ালেই মেয়েদের ছলনার কাহিনি মাকিনের তো না জানার কথা নয়। তারপর যখন দেখত ওই হাসি ছিল ছলনা তখন চুপ হয়ে যেত মাকিন। তার বেদনার কথা কাউকে বুঝতে দিত না। বোকার মতো শুধু হাসত আর দু চোখ দিয়ে পানি ঝরত। তাই ওর হাসি আর কান্নার পার্থক্য বোঝা ছিল কঠিন। কারও প্রতি রুষ্ট হলে বলত, ‘ব্যাটা একটা বদনা।’ শেষ পর্যন্ত বিয়ে হলো চট্টগ্রামে এবং সস্ত্রীক দেশত্যাগ করে চলে গেল কানাডায়। সেখানে একটি প্রাইভেট কলেজে প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপনা করত। তারপর বহু বছর পার হয়ে গেল এবং আমাদের মধ্যে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু দূরে গেলেই তো কাউকে ভোলা যায় না। তখন আরও বেশি করে বিচ্ছেদের বীণা বাজে। কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, বহু বছর পরে গ্রীষ্মের এক সকালে ভীষণভাবে মনে পড়তে লাগল মাকিনের কথা। হঠাৎ করেই ওর টেলিফোন নম্বরটা বার করে ফোন করলাম। ওপার থেকে ওর স্ত্রী টেলিফোন তুললেন এবং কাতর কণ্ঠে আমাকে বললেন, ‘আমি হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে কথা বলছি। একটু আগেও মাকিন আপনার কথা স্মরণ করেছে। আপনি তার সঙ্গে পারলে কথা বলুন। ওর শেষ নিশ্বাস বোধ হয় এখনি বেরিয়ে যাবে।’ মাকিনের স্ত্রী রেখা মোবাইল ফোনটি মাকিনের মুখে কাছে ধরেন। আমি এপাশ থেকে জোরে জোরে ‘মাকিন তুই ভালো হয়ে যাবি’ বলতে লাগলাম। ওপাশ থেকে অস্পষ্ট একটু গোঙানির আওয়াজ পেলাম। তার একটু পরেই মাকিনের সামনে থেকে ফোনটি নিয়ে রেখা বলল, ‘কলি ভাই, মাকিন আর বেঁচে নেই।’ যে বন্ধুর সাথে দশ বছর হয়নি কোনো যোগাযোগ, তার সাথে এমন কাকতালীয় সংযোগ ও বিচ্ছেদ আমার জীবনে আর ঘটেনি কখনো।

ঠিক এই সময় কয়েকটি ফিল্মে প্লে ব্যাক করার প্রস্তাব আসে এবং এর দুটিতে গাইতে রাজি হয়ে যাই। একটি ছিল ‘গোধূলীর প্রেম’ অন্যটি ছিল ‘জানাজানি’। ওখানে আমার সহশিল্পী ছিল আঞ্জুমান আরা বেগম। ওর বাড়ি বগুড়ায়। সংগীত পরিচালক ছিল সত্য সাহা। আঞ্জুমান আরার স্বভাবও ছিল খুব মিষ্টি। সে ছিল খুব নরম স্বভাবের মেয়ে। সুন্দর করে কথা বলতে পারত। ওদের বগুড়ার বাড়ির নাম ছিল হোয়াইট হাউজ। লিখেছিল, ‘এই হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট হয়ে আসবে কবে?’ বগুড়ায় যাওয়া হয়নি কোনো দিন। কোনো দিন হইনি কোনো হোয়াইট হাউজের প্রেসিডেন্ট।
রেডিওতে গান গাইতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল ফরিদা ইয়াসমিনের সাথে। আমাকে ভালো লেগে সে এগিয়ে ছিল অনেক দূর। কিন্তু ওই পর্যন্তই। রেডিওর তদানীন্তন অনুষ্ঠান নির্বাহী শামসুল হুদা চৌধুরীর আগ্রহে আলাপ হলো লায়লা আরজুমান্দ বানুর সাথে। মহিলা উর্দু ও পারশি গজল গাইতেন আর গাইতেন নজরুলসংগীত। বেশ ভালোই গাইতেন কিন্তু কণ্ঠস্বরটি খুব একটা মধুর ছিল না। আমিও যেহেতু গজল গাইতাম তাই আমাদের মধ্যে খুব দ্রুতই একটা সখ্য সৃষ্টি হলো। ওনার সিদ্দিক বাজারের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম তার আমন্ত্রণে গান শুনতে ও গাইতে। উনি আমার চেয়ে বয়সে অন্তত সাত আট বছরের বা তার চেয়েও বেশি বড় ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল আমার। একদিন নীরবে সরে আসি।
সাযযাদ হোসেনের সৌজন্যে নির্ধারিত সময়ের দু বছর পরে ইংরেজি বিভাগ থেকে এমএ পাস করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ইতি টানলাম। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির জন্য আবেদন করলাম। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের ইংরেজির প্রভাষক হিসেবে কাজে যোগদান করলাম এবং সেখানে এক বছর অধ্যাপনা করলাম। আমার সেজ ভাই আনিস-উদ-দৌলা সাহেব তখন চট্টগ্রামে ব্রিটিশ অক্সিজেন কোম্পানির ম্যানেজার। উনি তখনো বিয়ে করেননি। তার বাসাতেই থাকতাম। খাওয়াদাওয়া ফ্রি। এমনকি মাঝে মাঝেই তার গাড়িটিও আমার জন্য ফ্রি। তাই কলেজে যে মাইনে পেতাম (মাসিক দুশত আশি টাকা) তা গ্রহণ না করে দান করে দিতাম ছাত্রদের ‘পুওর ফান্ডে’। ছাত্রছাত্রীরা আমাকে খুবই ভালোবাসতো এবং আমার ক্লাসে পাঠ গ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ থেকে সদলবলে ছাত্রছাত্রীরা এসে ভিড় করত আমার ক্লাসরুমে। যে জন্য আমাকে প্রায়ই পড়াতে হতো কলেজের অ্যাসেম্বলি হলে। একদিন ভেজা বর্ষায় এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর সনেট পড়াচ্ছিলাম। বাইরে ছিল মুষলধারে বৃষ্টি। আমি পড়াতে পড়াতে অনেকদূর চলে গেছি। হঠাৎ দেখি আমার ক্লাসরুমে প্রিন্সিপাল সাহেব। পেছনের বেঞ্চে বসে কাঁদছেন।
বন্ধুরা সব একে একে সিএসপি পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে যোগ দিতে লাগল। বাঙালির মধ্যবিত্ত বাজারে সিএসপিদের তখন ভীষণ দাপট। বাড়ি থেকে আব্বা হুকুম করলেন যাতে আমি সিএসপি পরীক্ষা দেই। এই পরীক্ষা দেওয়ার অথবা এই চাকরিতে যোগদান করার কোনো ইচ্ছাই আমার জীবনে ছিল না। এদের অহঙ্কার আমি একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না। সিএসপি হওয়ার সাথে সাথেই মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালি ছেলেদের মানসে ঘটতো এক অদ্ভুত রূপান্তর এবং সেটাই ছিল আমার সবচেয়ে অপছন্দের জায়গা। আব্বার কথার অবাধ্য হইনি কখনো। তাই মেজ বু যখন পরীক্ষা দেওয়ার ফিস জমা দিলেন তখন আর আপত্তি করিনি আমি। এই চাকরির জন্য পরীক্ষা দেওয়াটা ছিল শুধুই পিতৃ নির্দেশ পালন। কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হলো পরীক্ষা। আমি জানতাম যে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ আমি হবই। রেজাল্ট বের হলো। পাস করলাম। মৌখিক পরীক্ষা হলো তাতেও উত্তীর্ণ হলাম। চিঠি এলো লাহোরে সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে এক বছর প্রশিক্ষণের জন্য যোগদানের নির্দেশ ছিল তাতে। এয়ারপোর্টে মা গেলেন, গেলেন বোনরাও। আর সেই সঙ্গে খোরশেদও। গত মাসে খোরশেদের পিআইএতে পাইলট হিসেবে চাকরি হয়নি সে মৌখিক পরীক্ষায় স্যুট পরেনি বলে। মা আমাকে এয়ারপোর্টে হাতে গুঁজে এক হাজার চারশত টাকা দিয়েছিলেন লাহোরে গিয়ে একটা স্যুট বানিয়ে নিতে। আমি সেই টাকাটা নীরবে খোরশেদের হাতে দিয়ে দিই আর বলি ‘তোর নেক্সট ইন্টারভিউতে স্যুট পরে যাবি”।
এলাম লাহোরে। এ শহরে এর আগে শুধু একবার এসেছিলাম ফিল্মে গান গাইতে। তাই শহরটি একেবারে অপরিচিত ছিল না। লাহোরের অভিজাত আপার মল এলাকায় অবস্থিত ছিল আমাদের সিভিল সার্ভিস একাডেমি। এই ভবনটি ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল তাদের শাসনামলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নবাব ও মহারাজাদের সাথে বৈঠকের জন্য। প্রায় একশত বিঘা এলাকা জুড়ে এর অবস্থান। এসেই পড়ে গেলাম প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক চাপে। রাতের অন্ধকারে ঘুম ভেঙে উঠতে হতো শারীরিক বিভিন্ন কসরতের জন্য। যেমন ড্রিল, দৌড়ানো, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ হালকাভাবে নিলে চলত না যেহেতু এগুলিতে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ছিল নম্বর- যা যোগ হতো মূল একাডেমিক নম্বরের সঙ্গে এবং এভাবেই নির্ধারিত হতো চূড়ান্ত সিনিয়রিটি। মাঝে মাঝে শীতের রাতে ব্যায়ামের ক্লাসে যোগদান করতে উঠতে হতো। ব্যায়ামের আলাদা পোশাক ছিল এবং সেই কাক ডাকা ভোরে উপস্থিত হতে হতো সেভ করে। ডেপুটি ডাইরেক্টর মিয়া রফিক উদ্দিন রীতিমতো গালে হাত দিয়ে দেখতেন ঠিকমতো সেভ করেছি কি না? না করলে সেদিনের জন্য অ্যাবসেন্ট বলে খাতায় উল্লেখ করা হতো। সকালের দৈনিক কসরত শেষ করার চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই একাডেমিক ক্লাস শুরু হতো একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে। আর ক্লাসরুমের দরজা একবার বন্ধ হলে আর খোলা হতো না। অতএব ড্রিলের কাপড় ছেড়ে গোসল সমাপ্ত করে স্যুট পরে ভোরের প্রাতঃরাশ খাবার সময় এতোই অল্প থাকত যে মাঝে মাঝে চা পর্যন্ত খাওয়ার সময় পেতাম না। ক্লাসরুমে আমার খুব ঘুম পেত। ডক্টর মালেক আর প্রফেসর ব্রাইবান্টির ক্লান্তিহীন বকবকানি শুনতে আর ভালো লাগত না। আবার প্রতিদিন আগের দিনের পাঠের ওপর আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হতো এবং যেখানে প্রাপ্ত নম্বরও যোগ হতো মূল একাডেমিক পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই অত্যাচারের মধ্যে থাকতে আর ভালো লাগত না। আমরা প্রায় সবাই হাঁফিয়ে উঠতাম। একাডেমির ডাইরেক্টর ছিলেন জনাব আগা আব্দুল হামিদ, যিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবের সচিব ছিলেন। তিনি ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি। ছিলেন স্বল্পভাষী ও অমায়িক। ছোটখাট মানুষ। কথাও বলতেন ক্ষীণ স্বরে। আমি ছিলাম তার খুব পছন্দের। এতটাই পছন্দের যে একদিন গাড়ি চালাবার জিপটা আমাকে সময় মতো দেয়নি বলে আমি ওই দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসারকে অকথ্য গালিগালাজ করি এবং সে হামিদ সাহেবের কাছে নালিশ দেয় আমার বিরুদ্ধে। ডাইরেক্টরের ছিল অসীম ক্ষমতা। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে তিনি যেকোনো প্রবেশনার অফিসারকে চাকরি থেকে বিদায় দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারতেন। আমার সৌভাগ্য যে আমার বিরুদ্ধে আগা আব্দুল হামিদ সাহেবের কাছে যে নালিশ পেশ করা হলো তা দেখে উনি শুধু একটি কথাই বললেন, ‘আসাফ্উদ্দৌলাহ্ এমন কাজ করতেই পারে না।’ বিষয়টি সেখানেই সমাপ্ত হয়। পরদিন একান্তে আমাকে তার বাসায় ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঘটনাটি সত্যি কি না? আমি তার স্নেহের কথা জানতাম বলেই বলেছিলাম, ‘স্যার, নালিশটি সত্যি।’ শুনে তিনি খুব হেসেছিলেন। দারুণ সংস্কৃতিমনা এই মানুষ ছিলেন খুব একা। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে বাড়িতে ডেকে ইংরেজি সাহিত্যের কবি ও সাহিত্যিকদের ব্যাপারে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করতেন। আর সব কথা শেষ হলে মীর্জা গালিব, মীর ত্বকি মীর, ইকবাল, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ অথবা আহমেদ ফরাজের গজল শুনতে চাইতেন। তার বাড়িতে ছিল এক পুরনো হারমোনিয়াম। তাই বাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনিয়েছি আমি তাকে। পাকিস্তানের বিখ্যাত মহিলা চিত্রশিল্পী জুবেদা আগা ছিলেন আগা আব্দুল হামিদের ছোট বোন। আমি এত শিক্ষিত, মার্জিত ও অভিজাত পরিবার জীবনে খুব কমই প্রত্যক্ষ করেছি।
আমার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখত এবং আমিও যতদূর সম্ভব চিঠিগুলোর উত্তর দিতাম। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে যেতাম আমার পশ্চিম পাকিস্তানের কলিগদের বাড়িতে তাদের আমন্ত্রণে। আর মাঝে মাঝেই যেতাম লাহোরের পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের অফিসে। সেখানকার পরিচালক ছিলেন পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। মার্কসবাদের ওপর তার ছিল ভীষণ আস্থা এবং তার কবিতাও ছিল মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত। অবাক করার কথা এই যে তার মার্কসবাদী কবিতার প্রশংসা ছিল কিন্তু ছিল না চর্চা। অথচ তার প্রেমের কবিতাগুলি উদ্বেলিত করেছিল লক্ষ হৃদয়। ‘দোনা যাহাঁমে তেরি মোহাব্বত মে হারকে, উও যা রাহাহে কই শবে গ্যম গুর্জা কে।’ ‘মুঝসে পহেলি সি মুহাব্বত মেরে মেহেবুব না মান, ম্যায়নে সামঝা কে তু হ্যায় তো দারাখশাঁয়ে হায়াত।’
জনাব ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে এই উপমহাদেশের সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি গল্প করতেন আমার সাথে। তিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাস সম্পর্কেও বলেছেন অনেক। একাত্তর সালে বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর অকথ্য বর্বরতাকে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ দারুণভাবে সমালোচনা করেছিলেন। ফয়েজ আহমেদ সাহেবকে যখন বলতাম আমাদের কঠোর এবং ক্লান্তিকর প্রশিক্ষণের কথা তখন তিনি একদিন বলেছিলেন ‘ইয়ে ভি উৎর জায়েগা’ সত্যি সত্যি লাহোরের ট্রেনিং দশ মাস পর সমাপ্ত হলো। ফিরে এলাম ঢাকায়।
ঢাকাকে এত সুন্দর মনে হয়নি আগে কখনো। কেননা দেশে ফেরাটা অনেকটা বাড়ি ফেরার মতো। এসেই আব্বা-মা-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ফরিদপুর। সবই আছে নেই শুধু আমার চিরপরিচিত খেলার সাথীরা। তারা কে যে কোথায় নিরুদ্দেশ, সে খবর পর্যন্ত আমার কাছে নেই। এখন নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে মাঠে। ওখানে থাকতেই জেনে গেলাম একাডেমির চূড়ান্ত পরীক্ষায় আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। আমার চেয়ে এক নম্বর বেশি পেয়ে আমার কাশ্মিরী বন্ধু মোহাম্মদ আহম্মেদ অধিকার করেছিল প্রথম স্থান। দূর থেকে দেখলাম আমার পুরনো স্কুল। যেখানে পড়ছে নতুন সব মুখ। সপ্তাহখানেক কাটিয়ে ফিরে এলাম ঢাকায়। সংস্থাপন বিভাগের পত্রে জানলাম আমার প্রথম পোস্টিং হয়েছে কুমিল্লায়। খুব খুশি হলাম। ঢাকার খুব কাছাকাছি আর প্লেনে আসতে সময় লাগে দশ মিনিট মাত্র। জয়েন করলাম। আমার প্রথম ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন সকলের অতি পরিচিত ওবায়দুল্লা খান, যাকে আমরা সবাই সেন্টু ভাই বলে ডাকতাম। সিভিল সার্ভিসে যোগদানের আগে সেন্টু ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ইংরেজি বিভাগেরই প্রভাষক হিসেবে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। আমরা তাকে ছয় মাসের মতো পেয়েছিলাম আমাদের শিক্ষক হিসেবে। তিনি ছিলেন একজন রোমান্টিক সজ্জন ব্যক্তি। অত্যন্ত বন্ধুসুলভ এবং প্রতিভাধর। আমার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সন্দ্বীপের কাজী এম এম হোসেন। তিনি বোধ হয় ১৯৫৪ ব্যাচের সিএসপি। আমার থাকার জায়গা নির্দিষ্ট হলো সার্কিট হাউজের একটি কামরায়। সার্কিট হাউজের উল্টো দিকেই ছিল কুমিল্লা স্টেশন ক্লাব। ওখানেই কাটত প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যা। যেহেতু ছোট্ট মফস্বল শহরে সন্ধ্যায় বিশেষ কিছু করার থাকে না সে জন্য ধীরে ধীরে তাস খেলা শিখলাম। সময়টা যেন কেটে যায়। কিছুদিনের মধ্যে আলাপ হলো কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব জনাব আখতার হামিদ খানের সঙ্গে। যেহেতু উর্দু শের শায়েরিতে আমার বিশেষ দক্ষতা ছিল সে জন্য ওনার সঙ্গেও খুব শের শায়েরি চলত। ফর্সা, দীর্ঘদেহী ও একধরনের সরল ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন আখতার হামিদ খান। তিনি ইংরেজ আমলের আইসিএস এবং তিনি আমাদের তখনকার ইস্ট পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি আলী আসগরের ব্যাচমেট ছিলেন। অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধকারী ছিলেন খান সাহেব। আমাকে বলেছিলেন যে পাঞ্জাবের আখড়ায় কুস্তিগিরদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত কুস্তি অভ্যাস করতেন। অবিভক্ত ভারতে তিনি আইসিএস পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং তার প্রথম পোস্টিং হয় পটুয়াখালীর এসডিও হিসেবে। মানুষের সেবা করার অদম্য বাসনা ছিল তার। চাকরির প্রথম দিকেই দেখলেন যে দম বন্ধ করা শৃঙ্খলার বাইরে গিয়ে মানুষের সেবা করা একজন সরকারি কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়। চাকরির প্রতি বিমুখ হয়ে তিনি পটুয়াখালী থাকতেই চাকরি থেকে ইস্তফা প্রদান করেন এবং মানুষের সেবায় নিজেকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। তিনি কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল পদে বেশ কিছুদিন চাকরি করেন। এখানে শিক্ষা প্রদান ছাড়াও সমাজসেবা করার সময় ও সুযোগ থাকত। ধীরে ধীরে তিনি কুমিল্লার সন্নিকটের গ্রামাঞ্চলের মানুষদের আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষিত করে তোলেন এবং এখান থেকেই সূচনা হয় তার পল্লী উন্নয়ন চিন্তা। কালক্রমে কুমিল্লার অভয়াশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এবং পরে সম্প্রসারিত হয়ে কোট বাড়িতে এই প্রতিষ্ঠানটি হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবী বিখ্যাত বার্ড (ইঅজউ) বা বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট। তার অবস্থানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা ও গবেষকবৃন্দ এই কুমিল্লা একাডেমিতে আসতেন শিক্ষাগ্রহণ করতে। একটি গ্রামের কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, বনায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে এক অপূর্ব সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনার নামই কুমিল্লা মডেল। বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হতো তাদেরই মধ্যে থেকে নেওয়া নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা। প্রত্যেক পেশার প্রতিনিধিত্ব থাকত এবং তারা তাদের আয়ের একটি ক্ষুদ্রাংশ দান করত তাদেরই উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট তহবিলে। এভাবে হতদরিদ্রদের দেওয়া হতো বিনাসুদে ঋণ। মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার প্রথম সার্থক প্রবর্তক ছিলেন আখতার হামিদ খান। দরিদ্র প্রতিভাবান ছাত্র ছাত্রীদের দেওয়া হতো স্কলারশিপ। এলাকার অসুস্থ রোগীদের দেওয়া হতো চিকিৎসা। কেনা হতো কৃষিকার্যে ব্যবহারের বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি। কৃষকদের শেখানো হতো লাইন ধরে বীজ বপন করা এবং সার ও পানির ব্যবহারের বিভিন্ন সময়সূচি। অচিরেই কুমিল্লার পার্শ¦বর্তী গ্রামগুলির চেহারা বদলাতে লাগল। ধান ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়তে লাগল এবং তাদের নতুন সচ্ছলতার প্রতিচ্ছবি স্পষ্টতর হতে লাগল। যেমন: খড় ও ছনের পরিবর্তে বাড়িগুলোর টিনের বাড়িতে রূপান্তর।
খান সাহেব আমার প্রতি ছিলেন অতি স্নেহশীল। সার্কিট হাউসে আমার কামরার পাশে এসে তাঁর ধূসর রঙের উইলিস জিপ থেকে হর্ণ বাজাতেন। এটা এত নিত্যনৈমিত্তিক হতে লাগল যে আমি হর্ণের আওয়াজেই বুঝতো পারতাম যে উনি এসেছেন। উনি নিজেই জিপ চালাতেন। আমাকে পাশে বসিয়ে নিয়ে যেতেন কখনো কাছের কখনো দূরের গ্রামে। সেখানে দেখাতেন একাডেমির পরামর্শে কৃষিকাজে কী আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একদিন খবর এল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ‘কুমিল্লা মডেল’ দেখতে আসবেন। জেলা প্রশাসনে আমরা তৎপর হয়ে ওঠলাম কীভাবে তাঁকে রিসিভ করা হবে। আখতার হামিদ খানের সঙ্গে অভয়াশ্রমে দেখা করার সময় কে কে সাথে যাবে এবং এছাড়া প্রেসিডেন্টের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো রয়েছেই। আইয়ুব খান পৌঁছালেন নির্ধারিত দিনে সকাল দশটায়। তাঁকে কুমিল্লা এয়ারপোর্টে রিসিভ করলেন ডেপুটি কমিশনার কে এম এম হোসেন। আমার সঙ্গেও পরিচয় হলো এই প্রথম। প্রচণ্ড সুদর্শন ছিলেন আইয়ুব খান। তার পরনে ছিল সাদা প্যান্ট ও একটা টুইলের ফুল হাতা সাদা হাওয়াই সার্ট। সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল আখতার হামিদ খান সাহেবেরও। কিন্তু আমরা কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারিনি। তিনি বললেন, ‘আমি এয়ারপোর্টে গিয়ে কী করব? তার চেয়ে অভয়াশ্রমে আমার অফিসেই আমি অপেক্ষা করব তাঁর।’ প্রেসিডেন্ট নামার একটু পরেই জিজ্ঞেস করলেন, ‘হয়্যার ইজ মিস্টার আখতার হামিদ খান?’ আমরা বললাম, ‘তিনি একাডেমি ভবনে আপনার জন্য অপেক্ষায় আছেন।’ প্রেসিডেন্ট বললেন, ‘আই ওয়ান্ট টু ভিজিট হিজ একাডেমি রাইট নাউ।’ নিয়ে গেলাম প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে। গিয়ে দেখি, সাদামাটা একটা চেয়ার টেবিলে বসে খদ্দরের পাঞ্জাবি পাজামা পরা অবস্থায় নিমের একটা মোটা ডাল দিয়ে দাঁত মাজছেন খান সাহেব। আমরা তার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তিনি আইয়ুব খানকে বললেন, ‘উইল ইউ হ্যাভ এ কাপ অফ টি অর উইল ইউ কাম উইথ মি টু সি দি পেডি ফিল্ডস।’ আইয়ুব খান বললেন, ‘লেট আস গো স্ট্রেইট টু ইউর ফেমাস পেডি ফিল্ডস।’ খান সাহেব তার সেই ধূসর জিপটিতে গিয়ে বসলেন চালকের সিটে আর প্রেসিডেন্টকে পাশে নিয়ে জিপ চালিয়ে চললেন তাকে আধুনিক সমবায়ভিত্তিক ধানের ক্ষেত দেখাতে। আসলে গ্রামীণ ব্যাংকের মূল উন্নয়ন দর্শন আখতার হামিদ খানের কুমিল্লা মডেলের কাছে গভীরভাবে ঋণী।
১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের দিকে বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় Letter to the Editor পাতায় এক বাঙালি পাষণ্ড জনাব আখতার হামিদ খানকে নিয়ে জঘন্য কিছু মন্তব্য লেখেন। তিনি অবাঙালি ছিলেন এটাই তার কাছে খান সাহেবের সবচাইতে বড় অপরাধ। একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার সাথে কাকতালীয় সাক্ষাৎ ঘটে আখতার হামিদ খান সাহেবের সঙ্গে মতিঝিলের পিআইএ হেড অফিসের ঠিক সামনে। আমি দৌড়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি অত্যন্ত বিষণ্ন মুখে আমাকে বললেন, ‘তুমি দেখোনি অবজারভারে কুমিল্লার এক ব্যক্তি আমার সম্পর্কে কীসব মনগড়া বিষাক্ত কথাবার্তা লিখেছে এবং অবজারভারও তা ছাপিয়েছে।’ কণ্ঠে এক আকাশ অভিমান নিয়ে বললেন, ‘আমি নাকি বাঙালি না এবং আমি নাকি দুর্নীতিপরায়ণ? কুমিল্লা একাডেমি করে আমি নাকি অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছি।’
অথচ আমি তো দেখেছি কী দারুণ সহজ ও সরল জীবন যাপন করতেন তিনি। তাঁর বসার ঘরে কার্পেট বা একটা সোফাসেট পর্যন্ত ছিল না। ছিল ছড়িয়ে থাকা কাঠের কিছু চেয়ার। যে কুমিল্লার মানুষের উন্নয়নের জন্য তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তার সম্পূর্ণ জীবন তার বিনিময়ে এই কি প্রাপ্য ছিল তার? এ-জাতির অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিতে গেলে লক্ষ পৃষ্টার এক বয়ান লিখতে হবে।
আবার এক অবাক করা দিনে আমার পোস্টিং হলো বার্ডের প্রধান হিসেবে। সৌভাগ্য হয়েছিল খান সাহেবের লেখা প্রবন্ধ সমগ্র ‘The works of Akthar Hamid Khan' বইটির মুখবন্ধ লেখার। সেটা ১৯৮৩ সালে। আমাকে বসতে হয়েছে খান সাহেবেরই রেখে যাওয়া চেয়ার টেবিলে। তার সময় সরকারের পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হতো কুমিল্লা একাডেমির পরামর্শে আর স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত হয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন বিভাগের কিছু উদাসীন কেরানিদের দ্বারা। কুমিল্লা একাডেমি বর্তমানে হয়েছে ঢাকার সরকারি কর্মকর্তাদের স্বপরিবারে যাবার একটা পিকনিক স্পট।
কুমিল্লায় আমার ডেপুটি কমিশনার কে এম এম হোসেন সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কখনোই মধুর হতে পারেনি। আসলে অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার মূলত একজন প্রবেশনার অর্থাৎ শিক্ষানবীশ। এই পোস্টিংটা চাকরিতে প্রশিক্ষণের একটি ধাপ। একদিন ডিসি সাহেবের সাথে বসে গল্প করছিলাম এমন সময় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ধর্মঘটরত ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দল দেখা করতে আসে ডিসি সাহেবের সাথে। ডিসি সাহেব তাদের ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন। ঘর প্রায় ভরে গেল ছাত্রদের দ্বারা। কলেজের এক ছাত্র নেতা কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়ার দাবি তুললেন। অত্যন্ত সংযত ভাষায় তিনি বললেন যে, ‘কলেজের নির্বাচন না দিলে এই ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে এবং প্রয়োজনে শহরে কঠোর হরতাল দেওয়া হবে।’ ডিসি সাহেব তাদের বললেন যে, তারা যদি হরতালের প্রোগ্রাম তুলে নিতে রাজি হয়, তাহলে তিনি বিষয়টি নিয়ে সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের সাথে আলোচনা করবেন এবং চেষ্টা করবেন যাতে কলেজের সংসদ নির্বাচন দিতে সরকার সম্মত হয়। তিনি ছাত্রদের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি চাইলেন। এটা বোধ হয় তাদের কাছে আগে থেকে তৈরি ছিল তাই তারা তাৎক্ষণিক সেটা ডিসি সাহেবের হাতের তুলে দিলেন, যাবার সময় তারা বলে গেল, ‘স্যার, আপনি আমাদের বিষয়টি সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। এই আশ্বাসে আমরা তিন দিনের জন্য হরতাল তুলে নিতে রাজি হলাম। আমাদের এই আস্থা আপনি রাখবেন বিশ্বাস করি।’
তারা কামরা ছেড়ে চলে যাবার সাথে সাথে ডিসি সাহেব ছাত্রদের লেখা স্মারকলিপিটি মুচড়িয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে ফেলে দিলেন। অবাক বিস্ময়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘স্যার আপনি ওদের দেওয়া স্মারকপত্রটি ফেলে দিলেন কেন?’ উত্তরে তিনি হেসে বলেছিলেন, ‘ছাত্রদের সংসদ নির্বাচন না দেবার সিদ্ধান্ত স্বয়ং গভর্নর মোনায়েম খানের। তিনি কোনোক্রমেই ছাত্রদের দাবি মানবেন না। সুতরাং ওই কাগজ ফেলে দেওয়াটাই তো সঠিক।’ আমি বললাম, ‘ওরা আপনার প্রতি এতটা বিশ্বাস রেখে হরতাল তুলে নিতে রাজি হলো আর আপনি তাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলেন?’ ডিসি সাহেব বললেন, ‘আসাফ্উদ্দৌল্লাহ্, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কিছুই তো এখনো শেখেননি? এখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর তা ভাঙার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এক্সপিডিয়েন্সি ইজ দি রুল অব দি গেম। এই ছাত্রদের নেতৃস্থানীয় যে কজন এসেছিল কালকের মধ্যে তাদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেব। আর ওদের মধ্যে থেকে কয়েকজন নেতাকে লাগিয়ে দেব ওদের ঐক্য ভেঙে দিতে। দেখি আবার হরতাল কী করে করে?’
সেদিনের অভিজ্ঞতা সরকারি চাকরির প্রতি আমার ঘৃণা বাড়িয়ে দিল বহুগুণে। তাহলে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানেই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সরলমতি মানুষদের বোকা বানানো? এক্সপিডিয়েন্সি কি জনসেবার মূল মন্ত্র? এই প্রশিক্ষণ নিয়েই কি আমি যাব উচ্চতর কর্মক্ষেত্রে আগামীর দিনগুলোতে? এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মোনাফেকি কখনই ব্যক্তিগত কিংবা রাষ্ট্রগত নীতি হতে পারে না। অফিসে দায়িত্ব কম তাই কাজও কম। তাস খেলে খেলে ক্লান্তি এসে গিয়েছিল।
ধীরেন দত্ত বাবুর বাড়িতে আমরা সবাই যেতাম। কুমিল্লার বিখ্যাত রানীর দিঘীর পাড়ে সুন্দর ছিমছাম একটি বাড়িতে থাকতেন তিনি। বাংলা ভাষার সপক্ষে পাকিস্তান জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে তার অগ্নিঝরা বক্তৃতা আমরা আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তার বড় ছেলে থাকতেন ঢাকায়। হেট টাই পরা এক বাঙালি ইংরেজ। আমার কবিতার পাশে তার ইংরেজি কবিতাও বাংলাদেশ অবজারভারের রোববারের সংখ্যায় প্রায় নিয়মিতই ছাপা হতো। তার স্ত্রী প্রতীতি দি ছিলেন এক অসামান্য মহিলা। তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ ছিলাম আমরা সবাই। সেন্টু ভাইও নিয়মিত ওখানে আড্ডা জমাতেন। তার একমাত্র কন্যা অ্যারোমা দত্ত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।
একদিন হঠাৎ করে ঠিক হলো যে কুমিল্লার সাংস্কৃতিক স্থবিরতা দূর করতে কিছু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। ঠিক হলো যে রবীন্দ্রনাথের ‘শ্যামা’ গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করা হবে কুমিল্লা টাউন হলে। আর আমাকে গাইতে হবে উত্তীয়’র সব গান। শুরু হলো রিহার্সাল প্রতীতিদির বাড়িতেই। সেন্টু ভাইয়ের স্ত্রী পুতুল হলো শ্যামা। পুতুল ঢাকা বিম্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী ছিল। আমাদের এক দুই বছরের জুনিয়র। এক মাস রিহার্সেলের পরে নির্ধারিত দিনে হল ভরা দর্শকদের সামনে কুমিল্লা টাউন হলে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় খুব সাফল্যের সাথে। এর কয়েক মাস পরে সংস্থাপন বিভাগ থেকে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয় মাগুরার এসডিও হিসেবে।
কুমিল্লা থেকে ঢাকায় ফিরে এক স্যুটকেস কাপড় নিয়ে আর কিছু প্রিয় বই, একটা রেকর্ড প্লেয়ার আর কিছু গানের ক্যাসেট সঙ্গী করে রওনা দিলাম মাগুরার পথে। যশোর বিমানবন্দরে দেখলাম আমার জিপটি এসেছে আমাকে মাগুরায় নিতে এবং বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মাগুরার সেকেন্ড অফিসার সাঈদ হোসেন। তিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের ভগ্নিপতি।
মাগুরা একটি প্রাচীন জনপদ। গ্রামাঞ্চলে অনেক বাউলের বাসা। তাদের বাড়িগুলো দেখলেই চেনা যেত। বাড়িগুলো চকচকে, ধবধবে। সন্ধ্যার পরে চাঁদ উঠলে তাদের বাড়ির লাউয়ের মাচার নিচে বসে অনুষ্ঠান হতো বাউল গানের। আমি মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে সাইকেলে করে গ্রামের আঁকাবাকা পথ দিয়ে পৌঁছে যেতাম সেই সব আলোছায়া ঘেরা বাউল গানের আসরে। ভাবতে অবাক লাগে যে আমি নিজেও মাঝে মাঝে বাউল গান গাইতাম। তাতে তারা ভীষণ উৎসাহ পেত এবং আমার গান শুনে তারা বুঝেছিল যে এ কোনো শখের শিল্পী নয়। যেহেতু আমি ছিলাম চর্চা করা এক শিল্পী তাই আমার গান শুনে তারা বিশ্বাস করতে পারত না যে আমি তাদের এসডিও বাহাদুর। আমি ছিলাম ব্যাচেলর। আমাকে খুশি করার জন্য মাগুরার টাউন সিনেমা হল থেকে সন্ধ্যা হলেই জোরে জোরে আমার রেকর্ডের গান বাজাতো। এতে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করতাম এবং এক ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে ওদের বলে পাঠালাম যেন আমার গান ভবিষ্যতে না বাজায়।
একদিন ট্যুর থেকে ফিরে মহকুমা আদালতের সামনে প্রাচীন এক বটগাছের নিচে এক বৃদ্ধা মহিলাকে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে দেখি। জিপ থেকে নেমে তার কাছে গেলাম এবং তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তার ছেলে-বৌয়ের কথায় উত্তেজিত হয়ে তাকে শারীরিক প্রহার করেছে। তিনি এর বিচার চান। একজন পুলিশ কনস্টেবলকে জিপে উঠিয়ে ওই বৃদ্ধাকে জিপে তুলে নিলাম। মাগুরা শহরের অদূরেই ছিল তাদের বাড়ি। বাড়িতে গিয়ে পেলাম তার ছেলেকে। তাকে তেতুল গাছের সঙ্গে বাঁধলাম। তাকে বেঁধে কনস্টেবলের হাত থেকে তার লাঠিটি নিয়ে প্রহার করতে লাগলাম ওই পাষণ্ডকে। পাষণ্ড ছেলেটি মার খেতে লাগল আর উচ্চস্বরে চিৎকার করতে লাগল। এক পর্যায়ে সেই বৃদ্ধা ক্ষিপ্ত হয়ে আমার দিকে তেড়ে এলেন। বললেন, ‘একটা নালিশ দিয়েছিলাম আপনার কাছে, তাই বলে ছেলেটাকে এভাবে পেটাবেন আপনি আমার সামনে?’ এই বলে তিনি আমাকে বেত মারা থেকে বিরত করলেন। ছেলেটির বাঁধন খুলে দিয়ে জিপে উঠে চলে এলাম। সারা পথ ভাবতে লাগলাম মায়ের মমতার কথা। ছেলে তাকে প্রহার করেছে কিন্তু সেই ছেলেকে আর কেউ প্রহার করবে, এটা তিনি মানতে রাজি নন। গল্প শুনেছিলাম যে এক পুত্র তার মাকে হত্যা করে মৃতদেহ ফেলে দিতে যাবার পথে হোঁচট খেয়ে যখন পড়ে যায় তখন নাকি বস্তার ভেতর থেকে তার মায়ের হৃৎপিণ্ড বলে উঠেছিল, ‘খোকা ব্যথা লাগেনি তো?’ আজ যেন তারই এক প্রতিচ্ছবি দেখত পেলাম। আমরা সন্তানেরা কি কোনো দিন বুঝতে পেরেছি মায়ের ভালোবাসা কতটা গভীর নিঃস্বার্থ মমতায় মোড়া?
ঠিক এ সময়ই হঠাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সেই দাঙ্গাতেই মারা যান আমার শিক্ষক অধ্যাপক বি.সি. রায়। আশেপাশের মহকুমাগুলিতেও ক্ষুদ্র আকারে দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। মাগুরায় যাতে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিছুতেই বিস্তার লাভ না করতে পারে সে জন্য প্রথম থেকেই আমি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশদের সতর্ক অবস্থানে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেই। খবর এল যে কাশ্মীরে ‘হজরত বালে’র অমর্যাদা হয়েছে বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। মাগুরার প্রধান মসজিদে জুম্মার দিন মওলানা সাহেব বক্তৃতায় ওই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মাগুরার মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানান।
আমি সেই মওলানা সাহেবের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করি। মুসলিম লীগের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পুত্র অনেক অস্ত্র সংগ্রহ করে একটি দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছে বলে পুলিশের সূত্রে খবর পেলাম। মহকুমার পুলিশ প্রধানকে অবিলম্বে ওই বাড়িটি সার্চ করে অস্ত্রগুলি উদ্ধার করার নির্দেশ দিলাম এবং কেউ বাধা দিলে তাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলাম। পুলিশ ওই বাড়িটিতে যখন ঢুকতে যায় তখন সেই নেতার পুত্র পুলিশকে ঢুকতে অস্ত্র হাতে বাধা প্রদান করে এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাড়ির ভেতর থেকে পাওয়া গিয়েছিল ৪০টি রামদা, গোটা চারেক বন্দুক ও কিছু গুলি। এই বন্দুক ও গুলিও ছিল লাইসেন্সবিহীন। আমার কাছে যখন জামিনের আবেদন করা হলো, আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। ভোরবেলা লাট সাহেবের টেলিফোন এল। জনাব মোনেম খানের সঙ্গে এর আগে আমার কোনো দিন কথা হয়নি। তিনি আমার কোনো কথাই শুনলেন না। বললেন, ওই মুসলিম লীগ নেতার গ্রেপ্তারকৃত পুত্রকে অবিলম্বে ছেড়ে দিতে। দুই ঘণ্টা পর টেলিফোন এল খুলনা থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব সবুর খানের। তিনিও আমাকে একই নির্দেশ দান করলেন। এরপরে টেলিফোন এল কমিশনার সাহেবের। কমিশনার ছিলেন জনাব আলী আহমেদ। তিনিও দিলেন একই নির্দেশ। এদের কারও কথা সেদিন আমি শুনিনি, যার জন্য পরের দিনই টেলিগ্রামের মাধ্যমে আমার বদলির আদেশ পাই।
আমি ব্যাচেলর মানুষ মাগুরায় এসেছিলাম একটি স্যুটকেস নিয়ে আর সাথে ছিল কিছু বই আর গানের ক্যাসেট। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নেওয়া আমার পক্ষে ছিল খুবই সহজ। এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার। এই ঘটনার দু-এক সপ্তাহ আগে কমিশনার আলী আহমেদ সাহেব খুলনা থেকে মাগুরায় এলেন। ডাকবাংলোয় আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘মুজিবুর রহমানের ভগ্নিপতি নাকি তোমার সেকেন্ড অফিসার? তুমি কি জানো সে ট্যুরে গিয়ে গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের জন্য চাঁদা তোলে? তার বার্ষিক এসিআরে (অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টে) এ কথা স্পষ্ট করে লিখে দিয়ো। তারপর আমরা দেখব ওর চাকরি থাকে কেমন করে!’ আমি উত্তরে বললাম, ‘স্যার, আমার সেকেন্ড অফিসারকে অদ্যাবধি আমি কোনো ট্যুরে পাঠাইনি। অতএব, ট্যুরে গিয়ে চাঁদা তোলার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ও কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ভালো রায় লেখে। অতএব আমার পক্ষে তার বিরুদ্ধে ওই সব অসমর্থিত কথা লেখা সম্ভব নয়।’ পরে অবশ্য সাঈদ আহমেদকে আমি কাজকর্মে আউটস্ট্যান্ডিং বলে এসিআর লিখি। আর এর ফলাফলস্বরূপ আমার এসিআরে কমিশনার সাহেব লিখেছিলেন, ‘He does not knwo hwo to write ACR’
আমি যখন বদলি হয়ে চলে যাবার জন্য সাদা অস্ট্রেলিয়ান জিপে যশোর বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দিই খবর পেয়ে তখন কয়েক শত মানুষ ভিড় করেছিল মাগুরা-ঝিনাইদহ সড়কে। অনেক বৃদ্ধা এসেছিলেন লাউ হাতে করে, কেউবা কলার ছড়ি হাতে নিয়ে। তাদের চোখে ছিল অশ্রু। আমার নতুন পোস্টিং হলো গণপূর্ত বিভাগে সেকশন অফিসার রূপে। এই সেকশন থেকে জমি বরাদ্দ দেওয়া হতো ধানমন্ডি, লালমাটি আবাসিক এলাকা, মতিঝিল বাণিজ্যি এলাকার প্লট আর চট্টগ্রামের আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লটসমূহ। প্লট প্রত্যাশীদের ভিড়ে দম ফেলার সময় পেতাম না। কাজে যোগদান করার পরদিনই আদেশ এল যে চিফ সেক্রেটারি আলী আসগর সাহেব তার সাথে সাক্ষাতের নির্দেশ দিয়েছেন। যথা সময়ে সচিবালয়ের ১ নম্বর ভবনে তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে পৌঁছালাম। একটু পরেই ডেকে পাঠালেন, তার ভাবসাব দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে তিনি আমার প্রতি বেশ বিরূপ। সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গভর্নর সাহেবের আত্মীয় জেনেও তুমি মাগুরায় ওই ব্যক্তিকে জামিন দাওনি কেন? আমি বলেছিলাম, স্যার, অপরাধীকে জামিন দেওয়া না দেওয়ার সম্পূর্ণ এখতিয়ার ট্রায়াল ম্যাজিস্ট্রেটের। সে সংক্ষুব্ধ হলে জেলা জজের আদালত থেকে জামিন নিতে পারে। আমি তার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে সেই মুহূর্তে জামিন দেওয়া ঠিক হবে না বলে মনে করেছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, ‘আমি তোমার সাথে এ নিয়ে তর্কে জড়াতে চাই না। তোমার জানা উচিত ছিল যে সরকারের ইচ্ছা প্রতিপালনই তোমার কর্তব্য।’ আমি বলেছিলাম, ‘স্যার, তাহলে তো সরকার আর রাষ্ট্রের পার্থক্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।’ তিনি রেগে গিয়ে বললেন, ‘তোমাকে জানতে হবে যে সরকারই রাষ্ট্র। কেননা তাদেরই দায়িত্ব সরকার পরিচালনার আর সেখানে ক্ষমতার বিভাজনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একাকার হয়ে যায় সরকারের ক্ষমতার কাছে।’ আমি নিরুত্তর রইলাম। রুমে শুধু এয়ারকন্ডিশনারের ক্ষীণ শব্দ আর আলী আসগর সাহেবের অসহ্য নীরবতা। মিনিটখানেক পরে একটা নথি নিয়ে কাজ করতে করতে গম্ভীর স্বরে চিফ সেক্রেটারি বললেন, ‘তুমি এখন আসতে পারো।’
সে সময়ে গভর্নর মোনায়েম খানের সচিব ছিলেন আমাদেরই সার্ভিসের জনাব আখলাক হোসেন। বাড়ি মাদ্রাজ। আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র। কী জানি কী কারণে তিনি ছিলেন আমার প্রতি খুবই স্নেহশীল। তিনি এর মধ্যে একদিন ফোন করে আমাকে জানালেন, যে ঢাকায় পাঠরত কিছু বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের বুড়িগঙ্গা নদীতে প্রমোদবিহারে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গভর্নর। তারা নাকি সাম্প্রতিক বন্যায় গভর্নর ফান্ডে তাদের বৃত্তির টাকা থেকে দান করেছেন। এই জন্য পুরস্কার হিসেবে গভর্নরের তাদের প্রতি এই বদান্যতা। আখলাক সাহেব চান, আমি গভর্নরের পক্ষ থেকে ছাত্র ছাত্রীদের এই প্রমোদ যাত্রায় উপস্থিত থাকি। নির্ধারিত দিনে ঢাকার সন্নিকটের পাগলা নৌঘাটে উপস্থিত হলাম। মেরি এন্ডারসন জাহাজে ঢাকা থেকে মুন্সীগঞ্জ এবং প্রত্যাবর্তন। জাহাজ ছাড়ার একটু পরে দেখি লাউঞ্জের কোনের এক টেবিলে তাস খেলা হচ্ছে এবং তার চারপাশে ভিড় করে আছেন অনেকে। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর নাফিস আহমেদ ও তার পরিবার। ওই টেবিলের দিকে যেতে দ্বিধা হচ্ছিল যেহেতু প্রফেসর নাফিস আহমেদ আমাদের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাকে ছাত্ররা বেশ সমীহ করত। এর মধ্যে আমার বন্ধু গভর্নরের পুলিশ এডিসি শরীফ আলী আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওই টেবিলের কাছে যারা ‘রামি’ খেলছিলেন। তারা আমাকে খেলায় যোগদান করতে অনুরোধ করেন। দর্শকের সারিতে আমার পাশের চেয়ারে বসা ছিলেন এক সুন্দরী সপ্রতিভ তরুণী। শরীফ আলী পরিচয় করিয়ে দিল যে ইনি প্রফেসর নাফিস আহমেদের একমাত্র কন্যা এবং সারা পাকিস্তানে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে আইয়ুব খান স্বর্ণপদক পেয়েছেন। আমার মনে পড়ল যে সংবাদটি আমি সম্প্রতি কাগজে পড়েছি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘রামি’ খেলতে জানেন কি না? তিনি বললেন ‘না’। আমি বললাম, ‘আপনি আমার তাসগুলো ধরুন, আমি এক্ষুণি শিখিয়ে দিচ্ছি।’ এই বাহানায় তার হাতটি ধরার সৌভাগ্য হলো। ঘণ্টাখানেক খেলার পরে তার টেলিফোন নম্বরটি নিলাম এবং বললাম, ‘আপনাকে আমি টেলিফোন করলে বিরক্ত হবেন না তো?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমাদের বাড়িতে মেয়েদের টেলিফোন ধরা নিষেধ।’ জিজ্ঞেস করলাম আর ফুলের তোড়া পাঠালে? তিনি মুচকি হেসে বললেন, ‘সেটাও সেন্সর বোর্ড পার হয়ে আমার কাছে পৌঁছাতে পারে আবার না-ও পারে।’ তার নাম জুলফিয়া আহমেদ। বাড়ি দিল্লির কাছে গুলোঠি শহরে। মাতৃভাষা বাংলা হলেও তিনি উর্দুতে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমার গান তো নিশ্চয়ই শুনেছেন?’ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, ‘না।’ এই তরুণীই কালক্রমে হয়ে যান আমার জীবনবঙ্গী।
ফিরে এলাম পাগলা ঘাটে। চলে গেলাম যে যার গন্তব্যে। পরদিনই অফিস থেকে জুলফিয়াকে টেলিফোন করি। টেলিফোন ধরলেন ওনার মা। তিনি ছিলেন খুব কড়া মেজাজের। জিজ্ঞেস করলেন, কী প্রয়োজনে আমি তার মেয়েকে ফোন করেছি? যেহেতু প্রয়োজনটা ছিল হৃদয়ের তাই সে কথা মুখে আনতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। তিনি ফোন মেয়েকে দিলেন না। ফোন রেখে দিলেন। পরদিন ঠিক ওই সময় আবার ফোন করলাম। সৌভাগ্যক্রমে এবার জুলফিয়া নিজেই ফোন ধরলেন। তাকে বললাম, ‘আপনার সঙ্গে কথা বলাই দুষ্কর। এত প্রশ্নের বাধা পেরিয়ে তবু তো পৌঁছালাম আপনার কাছে আজ।’ এভাবেই চলছিল। এর মধ্যে প্রতি সপ্তাহে এক নির্ধারিত দিনে ও সময়ে সচিবালয়ের উদ্যান থেকে জুলফিয়ার কাছে পৌঁছাতে লাগল ফুলের তোড়া। আমি জানি তিনি বাড়িতে বিব্রত হচ্ছেন আমার কারণে। কিন্তু ভালো লাগার উচ্ছ্বাস এতই অদম্য যে সে কে কী ভাবল তার পরোয়া করে না। বিব্রত হলে বিব্রত হোক। বিব্রত আমি করতেই থাকব। এমনি চলল মাস ছয়েক। ১৯৬৪ সালের এক প্রচণ্ড বৃষ্টির সন্ধ্যায় আমি ঢাকা ক্লাবে বসে মদ্য পান করছিলাম একা একা। হঠাৎ কী মনে হলো উঠে গিয়ে টেলিফোন করলাম জুলফিয়াকে। বললাম, ‘এমন ঘনঘোর বর্ষায় তোমাকে হয়তো বলা যায়, আমি ভালোবাসি। এই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে তুমি যদি তোমাদের বাড়ির গেটের পাশে উঁচু শিরিষ গাছের নিচে দাঁড়াতে পারো, তাহলে এক্ষুণি আমি এসে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, তুমি আসবে?’ আমাকে অবাক করে দিয়ে সে বলল, ‘তুমি যদি এতটা আসতে পারো, তাহলে আমি এতটুকু তো যেতেই পারি? তা যত বৃষ্টিই হোক না কেন!’ আমি তখন উড়ন্ত পাখির মতো আমার অস্টিন গাড়ি নিয়ে ছুটেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ নম্বর প্রফেসরস বাংলোর সামনে। গাড়ির হেড লাইটেই দেখতে পাই তাকে একেবারে বৃষ্টিধোয়া হয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়িটা পাশে রেখে দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভেতরে আসতে বললাম। আমার নিজের ঘর নাই। বাড়ি নাই কোথাও...।
শেষ অবধি আমার এই দুরবস্থা দেখে প্রখ্যাত আর্কিটেক্ট মাযহারুল ইসলাম ঠাঁই দিলেন। মিসেস ইসলাম ভেজা এক কাপড়ে আসা মেয়েটিকে পরতে দিলেন তার শাড়ি। পরদিন মাযহারুল ইসলাম সাহেবের পরিবাগের অফিসে মৌলভী ডেকে আমাদের বিয়ে পড়ানো হলো।
আমি বারবার বিপদে পড়ি। আর কেন জানি বিপদে পড়লেই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যায়। ঢাকায় যখন একেবারেই গৃহহীন ছিলাম তখনই আমার নতুন করে বদলি হলো রাজশাহীতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে। ওখানে আমার জন্য বাড়ির সুবন্দোবস্ত ছিল। প্রথমেই গিয়ে উঠলাম সার্কিট হাউজে এবং ওখানে মাস দুই থাকার পরে এডিসির বাড়িতে উঠলাম। হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি ও সামনে ছোট্ট সুন্দর লন। পেছনে আম ও লিচুর অনেকগুলো গাছ। বাড়িটি কালেক্টরেট থেকে তিন চার মিনিট হাঁটার পথ। আমার চাকরি জীবনে অন্যতম ট্রাজেডি ছিল খারাপ বস্দের দীর্ঘ তালিকা। রাজশাহীতে আমার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জামিলুর রহমান খান। তিনি ছিলেন অবিবাহিত, অবাঙালি, ঘোর বাঙালি বিদ্বেষি ও হীনমন্যতায় পরিপূর্ণ এক বাজে মানুষ।
প্রথমদিন থেকেই প্রায় প্রতিটি বিষয়েই তার সঙ্গে আমার মতভেদ শুরু হয়। অবশ্য ভাগ্যক্রমে বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে পেয়েছিলাম ১৯৪৯ ব্যাচের সিএসপি জনাব আবুল এহসানকে। তাঁর মতো অমায়িক, বিনয়ী ও বিচক্ষণ কর্মকর্তা আর খুব একটা দেখেছি বলে মনে হয় না। এদিকে জামিলুর রহমানের পদ্মা পাড়ের ডিসি হাউজে ঝুলতে লাগল নানা রঙের শাড়ি। যদিও তার না ছিল স্ত্রী, না কোনো বোন বা আত্মীয়া। কিছুদিন থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক হিস্ট্রি বিভাগের এক বৃদ্ধ প্রফেসরের শহরস্থ বাড়ির সামনে ডিসি সাহেবের জিপ রাতের পর রাত দেখা যেতে লাগল। ওই প্রফেসরের স্ত্রী ছিলেন এক অবাঙালি তরুণী। একদিন রাজশাহী কলেজের ছাত্ররা প্রফেসরের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ির সামনে ডিসির জিপ দেখে ওই জিপটিকে নোংরা আবর্জনা ও মলমূত্র দিয়ে ঢেকে ফেলে এবং প্রচণ্ড সোরগোল করতে থাকে। ডিসি জনরোষের ভয়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে আমাকে ফোন করেছিলেন ওই প্রফেসরের ফোন থেকে। কাতর কণ্ঠে আমাকে বললেন, ‘মুঝে বাঁচাও, ওয়ারনা ইয়ে লোগ মুঝে জান সে মার দেগা। প্লিজ, সেভ মি।’ বেটা বিপদে পড়েছে দেখে বেশ উৎফুল্ল বোধ করলাম। অত রাতে ড্রাইভার পাব কোথায়? নিজেই ড্রাইভ করে পৌঁছালাম সেই বাড়ির সামনে। গিয়ে দেখলাম ডিসির ড্রাইভার গাড়ির চাবি নিয়ে পালিয়ে গেছে নিজেকে বাঁচাতে। আমি ছাত্রদের অনেক অনুরোধ করে ওখান থেকে চলে যেতে বলি এবং তারা বিষয়টি কমিশনার সাহেবকে জানানো হবে এই শর্তে ওখান থেকে চলে যায়। আমি ধীরে ধীরে ওই বাড়ির কড়া নাড়ি এবং দেখি এক বিধ্বস্ত জামিলুর রহমান খানকে। যেহেতু তার ল্যান্ডরোভারটি মলমূত্রে আচ্ছাদিত ছিল আর ড্রাইভারও ভয়ে গেছিল পালিয়ে তাই তাকে আমার জিপে করে ডিসি হাউসে পৌঁছে দেই।